মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এর শুরুতে মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের ফলে ১২০১- ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত সংস্কৃতিতে যে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে তাতে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয়নি বলে এ সময়কালকে সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলে ।
১৩৫০ সালের পরবর্তী সময়ে বাংলা কাব্যের দুটি প্রধান ধারা পরিলক্ষিত হয়। একটি হলো কাহিনীকাব্য; অপরটি হলো গীতিকাব্য। প্রথম ধারার কাহিনী কাঠামোর মধ্যে সংগীতধর্মিতা লক্ষণীয়। দ্বিতীয় ধারার প্রধান লক্ষণ গীতধর্মিতা ও ভাবধর্মিতা। মধ্যযুগের প্রথম কাব্য ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ এবং শ্রেষ্ঠ কাব্য ‘বৈষ্ণব পদাবলি’
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
প্র. মধ্যযুগের সময়কাল কত?
উ. ১২০১-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র. মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান ধারা কয়টি?
উ. ৪টি। যথা: ক. মঙ্গলকাব্য, খ. বৈষ্ণব পদাবলি, গ. রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান, ঘ. অনুবাদ সাহিত্য।
প্র. মধ্যযুগের কোন সময়কে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণালি সময় বলা হয়?
উ. মোগল যুগ।
চৈতন্যদেবের জীবনী ভিত্তিক যুগবিভাগ
ক. প্রাকচৈতন্য যুগ (১২০১-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ),
খ. চৈতন্য যুগ (১৫০১-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ),
গ. চৈতন্য পরবর্তী যুগ (১৬০১-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ)।
মুসলিম শাসনামল ভিত্তিক যুগবিভাগ
ক. তুর্কি যুগ (১২০১-১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ), খ. সুলতানি যুগ (১৩৫১-১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দ),
গ. মোগল যুগ (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে, মধ্যযুগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
১. পাঠান আমল (১২০১-১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ),
২. মুঘল আমল (১৫৭৭-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ)।
অন্ধকার যুগ (১২০১-১৩৫০)
১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের ফলে বাংলার প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কৃতিতে বড় পরিবর্তন ঘটে। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধশক্তির নেতৃত্ব চলে যায় মুসলমানদের হাতে। নেতৃত্ব পরিবর্তনে সাময়িকভাবে সৃষ্ট এই বিমূঢ় অবস্থার প্রেক্ষিতে তেমন কোনো সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি, তাই ঐতিহাসিকদের মতে, এ সময়কে অন্ধকার যুগ বলে ।
প্র. বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগের ব্যাপ্তি কত?
উ. ১২০১-১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ (তুর্কি শাসনামল)। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
প্র. অন্ধকার যুগের সাহিত্যকর্মগুলো কী কী?
উ. ‘প্রাকৃতপৈঙ্গল’: এটি ত্রয়োদশ শতকে প্রাকৃত ভাষায় শ্রীহর্ষ রচিত গীতিকবিতার মহাসঙ্কলন যা অন্ধকার যুগের প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন ।
‘শূন্যপুরাণ’: এটি রামাই পণ্ডিত রচিত ৫১টি অধ্যায় সম্বলিত সংস্কৃত ভাষায় গদ্য পদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য। এর মূল নাম পাওয়া যায়নি, তাই নগেন্দ্রনাথ বসু রামাই পণ্ডিতের ভূমিকায় পাওয়া শূন্যপুরাণ অনুসারে এর নাম রাখেন ‘শূন্যপুরাণ’ বা এতে শূন্যময় দেবতা ধর্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতির বর্ণনা আছে বলেই এর নাম রাখা হয় ‘শূন্যপুরাণ’।
‘নিরঞ্জনের রুষ্মা’ বা ‘নিরঞ্জনের উষ্মা’ এ কাব্যের অংশ বিশেষ। নগেন্দ্রনাথ বসু তিনটি পুঁথিপাঠ সংগ্রহ করে ‘শূন্যপুরাণ’ নামে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ থেকে এটি প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এবং হিন্দুদের লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে।
এ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘নিরঞ্জনের রুষ্মা’ বা ‘নিরঞ্জনের উষ্মা’ কবিতায় ব্রাহ্মণ্য শাসনের বদলে মুসলিম শাসন প্রচলনের পক্ষে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। ‘সেক শুভোদয়া’: রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় গদ্য পদ্যে (চম্পুকাব্য) ২৫টি অধ্যায়ে এটি রচনা করেন।
শেখের শুভোদয় অর্থাৎ শেখের গৌরব প্রচারই এর মূল উপজীব্য। এ গ্রন্থে মুসলমান দরবেশের চরিত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, যা বাংলা ভাষায় রচিত পীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।এখানে বর্ণিত প্রেমসংগীতটিকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র প্রেমসংগীত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
প্র. বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলতে কী বুঝায়? (৪৩/৩০তম বিসিএস লিখিত]
উ. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০১-১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে অন্ধকার যুগ বলে। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলা দখলের ফলে সমাজে নানা ধরনের অস্থিরতার সৃষ্টি হওয়ার কারণে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারেনি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
ওয়াকিল আহমদের মতে, ‘প্রথমে সেন ও পরে পাঠান আমলে সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পটভূমি পরিবর্তিত হলে সহজিয়া সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ঘটে। ফলে তাদের ধর্মসাধনা ও জ্ঞানসাধনা রুদ্ধ হয়; সেই সাথে বাংলা সাহিত্য চর্চার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, কেননা ঐ যুগে সহজিয়াগণই বাংলা ভাষার একমাত্র ধারক ও বাহক ছিলেন’ ।
তবে অনেক সাহিত্যিকের মতে, সে সময়ে বিশেষ কোনো সাহিত্য পাওয়া না গেলেও ‘শূন্যপুরাণ’, শুভোদয়া’ প্রভৃতি সাহিত্য রচিত হয়েছিল। যেহেতু দু’একটা গ্রন্থের উপর নির্ভর করে একটি সময়কে নির্ণয় করা দুষ্কর, তাই এ সময়কে অন্ধকার যুগ বলে ।
এক কথায় বলা যায়, এ সময়কালে যে তিনটি গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলোর কোনোটিই বাংলা ভাষায় রচিত ছিল না। যেহেতু যুগকে ভাগ করা হয়েছে বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের অনুপস্থিতির জন্য এ সময়কালকে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলে। (যদিও এটি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে)।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
সর্বজনস্বীকৃত খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত মধ্যযুগের প্রথম কাব্য ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’। এটির রচয়িতা মধ্যযুগের আদি বা প্রথম কবি বড়ু চণ্ডীদাস। হাতে লেখা পুঁথিখানির প্রথমে দুটি পাতা, মাঝখানে কয়েকটি পাতা ও শেষের পাতাটি নেই।
পুঁথিখানিতে গ্রন্থের নাম, রচনাকাল ও পুঁথি-নকলের দিনক্ষণ কিছুই উল্লেখ নেই। এজন্য কবির পরিচয়, গ্রন্থনাম ও রচনাকাল অংশ পাওয়া যায়নি। তবে পুঁথির সাথে একটি চিরকুট পাওয়া গিয়েছে, তাতে ‘শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব’ বলে একটা কথা লিখিত আছে। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নামটি রাখেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।
প্র. ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের রচয়িতা কে? ১৫তম বিসিএস লিখিত
উ. ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
প্র. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কোথা থেকে কে উদ্ধার করেন? (২৫তম বিসিএস লিখিত]
উ. ১৯০৯ সালে (১৩১৬ ব.) পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাকিল্যা (কালিয়া) গ্রামের শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়ির গোয়ালঘরের মাচার ওপর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং পুঁথিশালার অধ্যক্ষ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এটি উদ্ধার করেন । বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি- ‘বিদ্বদ্বল্লভ’।
প্র. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল কত? [১৫তম বিসিএস লিখিত]
উ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে, ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ। গোপাল হালদারের মতে, ১৪৫০-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।
প্র. কার সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হয়?
উ. বসন্তরঞ্জন রায় ১৯১৬ সালে (১৩২৩ ব.) ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ থেকে এটি প্রকাশ করেন। বর্তমানে এটি ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্ল রায় (কলকাতা) রোডের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় সংরক্ষিত আছে।
প্র. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কয়টি খণ্ড ও চরিত্র আছে?
উ. ১৩টি খণ্ড। যথা: ১. জন্ম খণ্ড, ২. তাম্বুল খণ্ড, ৩. দান খণ্ড, ৪. নৌকা খণ্ড, ৫. ভার খণ্ড, ৬. ছত্র খণ্ড, ৭. বৃন্দাবন খণ্ড, ৮. কালিয়দমন খণ্ড, ৯. যমুনা খণ্ড, ১০. হার খণ্ড, ১১. বাণ খণ্ড, ১২. বংশী খণ্ড, ১৩. বিরহ খণ্ড ।
চরিত্র: রাধা (জীবাত্মা বা প্রাণীকুল), কৃষ্ণ (পরমাত্মা বা ঈশ্বর) ও বড়ায়ি (রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতি) ।
উ. ‘শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ’। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নামটি রাখেন বসন্তরঞ্জন
প্র. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অপর নাম কী?
উ. রায় বিদ্বদ্বল্লভ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
প্র. ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের পরিচয় দাও। (৩৩তম বিসিএস লিখিত]
উ. বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সুপরিচিত কবি বড়ু চণ্ডীদাস ভাগবতের কাহিনী কে অবলম্বন করে, কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কাহিনী, জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রভাব কে আমলে নিয়ে, লোকসমাজে প্রচলিত রাধা-কৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কিত গ্রাম্য গল্পের সাহায্য ৪১৮টি পদ, ১৬১টি শ্লোক ও ১৩টি খণ্ডের মাধ্যমে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য রচনা করেন।
১৯০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এটি উদ্ধার করেন। পরে বসন্তরঞ্জন রায় ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ থেকে এটি প্রকাশ করেন।
কাব্যের নায়ক কৃষ্ণ, কিন্তু সে ধর্মগ্রন্থের দেবতা কৃষ্ণ নয়। সে দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন, স্থুল, তীব্র আবেগের কিশোর কৃষ্ণ। নায়িকা রাধা প্রবল কামাসক্ত ও সম্ভোগলিপ্স পরিহাসপ্রিয় জীবনময়ী। নারী। নপুংশক আইহনের সঙ্গে বিবাহিত জীবনে অতৃপ্ত একজন গোপকিশোরী রাধার আর্তি-হাহাকার, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের সমাজনন্দিত প্রেমকাহিনী হচ্ছে কৃষ্ণ ও রাধাকে নিয়ে লেখা প্রথম কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল উপজীব্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
আধ্যাত্মিক বা দর্শন কিংবা দেবলীলা নয়, পৌরাণিক উপাদান নির্ভর হয়েও ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ লৌকিক প্রণয় আকাঙ্ক্ষা আর মানবলীলাকেই মুখ্য করে তুলেছে। এ কাব্যে কৃষ্ণের পূর্বরাগ থেকে আরম্ভ করে প্রেমে নিমজ্জিত ও কৃষ্ণ-কাতর রাধাকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের মথুরায় গমন পর্যন্ত কাহিনী বিদ্যমান ।
প্র. ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের গঠনরীতি কোন ধরনের?
উ. ‘শ্ৰীকৃষ্ণকীর্তন’ মূলত একটি যাত্রাপালা ছিল বলে মনে করা হয়। কারণ, কাব্যটি সংস্কৃত গীতগোবিন্দের অনুরূপ গীতি এবং সংলাপবহুল নাট্যলক্ষণাক্রান্ত রচনা বলে অনেক পণ্ডিত একে নাট্যগীতিকাব্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
ড. বিমানবিহারী মজুমদার একে ‘রাধাকৃষ্ণের ধামালী’ বলে অভিহিত করেছেন। ধামালি কথাটির অর্থ- রঙ্গরস, পরিহাস বাক্য, কৌতুক। রঙ্গ তামাসার কালে কপট দম্ভ প্রকাশ করে। যে সব উক্তি করা হয়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাকে ধামালী বলে। নাটপালায় এরূপ ধামালী হাস্যরসের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। এ কাব্যে মোট বারটি স্থানে ধামালী কথাটির প্রয়োগ আছে।
প্র. ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে লিখ। (৪০তম বিসিএস লিখিত]
উ. নিম্নে খণ্ড অনুযায়ী কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো: জন্ম খণ্ড : কৃষ্ণ ও রাধা উভয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় মর্ত্যে মানবরূপে জন্ম নিয়েছে। কৃষ্ণ পাপী কংস রাজাকে বধ করার জন্য দেবকী ও বাসুদেবের সন্তান হিসেবে জন্ম নেয়। জন্মের পরেই বাসুদেব গোপনে কৃষ্ণকে অনেক দুরে বৃন্দাবনে জনৈক নন্দ গোপের কাছে রেখে আসে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
সেখানেই দৈব ইচ্ছায় রাধা আরেক গোপ সাগর গোয়ালার স্ত্রী পদ্মার গর্ভে জন্ম নেয়। দৈব নির্দেশেই বালিকা বয়সে নপুংসক আইহন বা আয়ান গোপের সঙ্গে রাধার বিয়ে হয়। আয়ান গোচারণ করতে গেলে রাধাকে বৃদ্ধা পিসি বড়ায়ির তত্ত্বাবধানে রাখা হয় ।
তাম্বুল খণ্ড: অন্য গোপ বালিকাদের সাথে রাধা মথুরাতে দই- দুধ বিক্রি করতে যায়। বড়ায়িও যায় তার সাথে। বৃদ্ধা বড়ায়ি পথে রাধাকে হারিয়ে ফেলে এবং রাধার রূপের বর্ণনা দিয়ে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করে, এমন রূপসীকে দেখেছে কিনা? রাধার রূপের বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ পূর্বরাগ অনুভব করে। সে বড়ায়িকে বুঝিয়ে রাধার জন্য পান ও ফুলের উপহারসহ প্রস্তাব পাঠায়।
কিন্তু বিবাহিতা রাধা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে । দান খণ্ড: কৃষ্ণ দই-দুধ বিক্রির জন্য মথুরাগামী রাধা ও গোপীদের পথ রোধ করে। তার দাবী নদীর ঘাটে পারাপার- দান বা শুল্ক দিতে হবে, অন্যথায় রাধার সঙ্গে মিলিত হতে দিতে হবে।
রাধা কোনভাবেই এ প্রস্তাবে রাজি হয় না । এদিকে তার হাতে কড়িও নেই। রাধা নিজের রূপ কমাবার জন্য চুল কেটে ফেলতে চাইলো; কৃষ্ণের হাত থেকে বাচার জন্য বনে দৌড় দিল। কৃষ্ণ পিছু ছাড়বার পাত্র নয়। অবশেষে কৃষ্ণের ইচ্ছায় কর্ম হয় ।
নৌকা খণ্ড: পরবর্তীতে রাধা কৃষ্ণকে এড়িয়ে চলে। কৃষ্ণ নদীর মাঝির ছদ্মবেশ ধারণ করে। একজন পার করা যায় এমন একটি নৌকাতে রাধাকে তুলে সে মাঝ নদীতে নৌকা ডুবিয়ে দেয় এবং রাধার সানিদ্ধ লাভ করে। নদীর তীরে উঠে, লোকলজ্জার ভয়ে রাধা তার সখীদের বলে যে, নৌকা ডুবে গিয়েছে, কৃষ্ণ আপ্রাণ চেষ্টা করে তার জীবন বাঁচিয়েছে, কৃষ্ণর অনুপস্থতিতে সে ডুবে মারা যেত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
ভার খণ্ড: শরৎকালে শুকনো পথঘাট, তাই হেঁটেই মথুরাতে গিয়ে দুধ-দই বিক্রি করা যায়। কিন্তু রাধা আর বাড়ির বাইরে আসে না। আগের ঘটনাগুলো সে শাশুড়ি বা স্বামীকেও ভয়ে ও লজ্জায় খুলে বলেনি। রাধার অনুপস্থিতিতে কৃষ্ণ বিষণ্ণ।
সে বড়ায়িকে মাধ্যমে রাধার শাশুড়িকে বোঝায় যে, ঘরে না বসে থেকে, রাধা দই-দুধ বিক্রি করে কিছু পয়সা তো রোজগার করতে পারে। শাশুড়ির আদেশ মতো রাধা বাইরে বের হয়। কিন্ত প্রচণ্ড রোদের কারণে তার কোমল শরীরে দুধ-দই বহন করে রাধা অনেক ক্লান্ত হয়ে যায়।
এসময় কৃষ্ণ ছদ্মবেশে মজুরি করতে আসে। পরে ভার বহন অর্থাৎ মজুরির বদলে রাধার আলিঙ্গন কামনা করে। রাধা এই চতুরতা বুঝতে পারে। সে কাজ আদায়ের লক্ষ্যে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। তাই কৃষ্ণ আশায় বুক বাধে এবং রাধার পিছু পিছু ভার বহন করে মথুরা পর্যন্ত নিয়ে আসে।
ছত্র খণ্ড: দুধ-দই বেচে মথুরা থেকে এবার ফেরার পালা। কৃষ্ণ তার প্রাপ্য আলিঙ্গন চাইছে। রাধা চালাকি করে বলে, ‘এখনো প্রচণ্ড রোদ। তুমি আমাদের মাথায় ছাতা ধরে বৃন্দাবন পর্যন্ত চলো। পরে দেখা যাবে।’ কৃষ্ণ ছাতা ধরতে লজ্জা ও অপমান বোধ করছিল। তবু আশা নিয়েই কৃষ্ণ ছাতা ধরেই চলল । কিন্তু তার আশা পূর্ণ করেনি রাধা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
বৃন্দাবন খণ্ড: রাধার বিরুদ্ধ আচরণ কৃষ্ণের ভাবান্তর ঘটায় । সে অন্য পথ অবলম্বন করে। কৃষ্ণ কটু বাক্য না বলে, দান বা শুল্ক আদায়ের নামে বিড়ম্বনা না করে, বরং বৃন্দাবনকে অপূর্ব শোভায় সাজিয়ে তুলে। রাধা ও গোপীরা সেই শোভা দর্শন করে কৃষ্ণের উপর রাগ ভুলে যায়।
কৃষ্ণ সব গোপীকে দেখা দেয়। পরে রাধার সঙ্গে তার দর্শন ও মিলন হয়। কালিয়দমন খণ্ড: যমুনা নদী বৃন্দাবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে । এ যমুনা নদীতে কালিয়নাগ বসবাস করে। কালিয়নাগের বিষে যমুনার পানি বিষাক্ত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
কৃষ্ণ কালিয়নাগকে তাড়ানোর জন্য নদীর পানিতে ঝাঁপ দেয়। দৈব ইচ্ছায় ও কৃষ্ণের বীরত্বে কালিয়নাগ পরাজিত হয় এবং দক্ষিণ সাগরে বসবাস করতে যায়। কালিয়নাগের সঙ্গে কৃষ্ণ যখন জলযুদ্ধে লিপ্ত তখন রাধার বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় ।
যমুনা খণ্ড: রাধা ও গোপীরা যমুনাতে জল আনতে যায়। কৃষ্ণ যমুনার জলে নেমে হঠাৎ ডুব দিয়ে আর ওঠে না। সবাই মনে করে কৃষ্ণ ডুবে গেছে। কিন্তু কৃষ্ণ লুকিয়ে কদম গাছে বসে থাকে । রাধা ও সখিরা জলে নেমে কৃষ্ণকে খুঁজতে থাকে। কৃষ্ণ নদীতীরে রাধার খুলে রাখা হার চুরি করে আবার গাছে গিয়ে বসে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
হার খণ্ড: রাধা কৃষ্ণের চালাকি বুঝতে পারে। হার না পেয়ে রাধা কৃষ্ণের পালিতা মা যশোদার কাছে নালিশ করে । কৃষ্ণও মিথ্যে বলে মাকে। কৃষ্ণ বলে, ‘আমি হার চুরি করব কেন, রাধাতো পাড়ার সম্পর্কে আমার মামি।’ বড়ায়ি সব বুঝতে পারে এবং রাধার স্বামী আয়ান হার হারানোতে যাতে রাগান্বিত না হয় সেজন্য বলে যে, ‘বনের কাঁঠায় রাধার গজমতির হার ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গেছে।’
বাণ খণ্ড: কৃষ্ণ রাধার উপর ক্রুদ্ধ হয় মায়ের কাছে নালিশ করার জন্য। রাধাও কৃষ্ণের প্রতি প্রসন্ন নয়। বড়ায়ি বুদ্ধি দিলো, কৃষ্ণ যেন শক্তির পথ পরিহার করে মদনবাণ প্রেমে রাধাকে বশীভূত করে। সে মতো কৃষ্ণ ফুল নিয়ে কদমতলায় বসে। রাধা কৃষ্ণের প্রেমবাণে আটকা পড়ে। এরপর কৃষ্ণ রাধাকে চৈতন্য ফিরিয়ে দেয় এবং রাধা কৃষ্ণ এর প্রেমে পড়ে যায় এবং কৃষ্ণকে চোখে হারায়।
বংশী খণ্ড: কৃষ্ণ রাধাকে আকৃষ্ট করার জন্য সময়-অসময়ে বাঁশিতে সুর তোলে। কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধার রান্না এলোমেলো হয়ে যায়, মন কুমারের চুল্লির মতো পুড়তে থাকে, রাত্রে ঘুম আসে না। ভোর বেলা কৃষ্ণ অদর্শনে রাধা মূর্ছা যায়। বড়ায়ি রাধাকে পরামর্শ দেয়, সারারাত বাঁশি বাজিয়ে সকালে কদমতলায় কৃষ্ণ বাঁশি শিয়রে রেখে ঘুমায় । তুমি সেই বাঁশি চুরি করো, তবেই সকল সমস্যার সমাধান হবে। বড়াইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী রাধা কাজ করে।
কিন্তু কৃষ্ণ বুদ্ধিমান, যার জন্য সে বাঁশি চোর কে খুব সহজে বুঝে ফেলে। বড়ায়িকে স্বাক্ষী রেখে রাধা কৃষ্ণকে প্রতিজ্ঞা করতে বলে যে, ‘সে কখনো রাধার কথার অবাধ্য হবে না এবং রাধাকে কখনোই ত্যাগ করবে না, তবেই বাঁশির সন্ধান মিলতে পারে।’ কৃষ্ণ কথা দেয় এবং নিজের বাঁশি ফিরে পায় ।
বিরহ খণ্ড: তারপর কৃষ্ণ রাধার উপর উদাসীনতা প্রকাশ করে । মধুমাস সমাগত, তাই রাধা বিরহ অনুভব করে। রাধা বড়ায়িকে বলে, কৃষ্ণকে এনে দিতে। দুধ-দই বিক্রির ছল করে রাধা নিজেও কৃষ্ণকে খোঁজার জন্য বের হয়।
অবশেষে বৃন্দাবনে বাঁশি বাজানো অবস্থায় কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ রাধাকে বলে, ‘তুমি আমাকে নানা সময় লাঞ্ছনা করেছো, ভার বহন করিয়েছো, মায়ের কাছে আমার নামে বিচার দিয়েছো, তাই তোমার উপর আমার মন উঠে গেছে।’ রাধা বলে, ‘তখন আমি বালিকা ছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর।
আমি তোমার বিরহে মৃতপ্রায়। তির্যক দৃষ্টি হলেও তুমি আমার দিকে তাঁকাও।’ কৃষ্ণ বলে, ‘বড়ায়ি যদি আমাকে বলে যে তুমি রাধাকে প্রেম দাও, তাহলে আমি তোমার অনুরোধ রাখতে পারি।’ অবশেষে বড়ায়ি রাধাকে সাজিয়ে দেয় এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়।
রাধা ঘুমিয়ে পড়লে কৃষ্ণ রাধাকে রেখে কংস বধ করার জন্য মথুরাতে চলে যায়। ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণকে না দেখে রাধা আবার বিরহকাতর হয়ে পড়ে। রাধার অনুরোধে বড়ায়ি কৃষ্ণের সন্ধানে যায় এবং মধুরাতে কৃষ্ণকে পেয়ে অনুরোধ করে, ‘রাধা তোমার বিরহে মৃতপ্রায়। তুমি উন্মাদিনীকে বাঁচাও। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
কিন্তু কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যেতে চায় না এবং রাধাকে গ্রহণ করতেও চায় না। কৃষ্ণ বলে, ‘আমি সব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু কটুকথা সহ্য করতে পারি না। রাধা আমাকে কটুকথা বলেছে।’ (‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য এখানেই ছিন্ন। পরবর্তী পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। তাই এ গ্রন্থের সমাপ্তি কেমন তা জানা যায় না।)
বৈষ্ণব পদাবলি
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৈষ্ণব পদাবলি, যা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত। চতুর্দশ শতকের শেষদিকে এগুলো কবিতা আকারে রচিত হতে থাকে। কোনো বিশেষ ধর্মীয় আবেগে রচিত হয়নি বৈষ্ণব পদাবলি।
শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রচার করেন ‘বৈষ্ণব ধর্ম’ এবং এর পর থেকে বাংলা কবিতায় বৈষ্ণব দর্শন স্থান পেতে থাকে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই সৃষ্টিসম্ভার প্রাচুর্য ও উৎকর্ষপূর্ণ ছিল। এর বিষয়বস্তু হলো রাধা ও কৃষ্ণের (রূপকাশ্রয়ে ভক্ত ও ভগবান) প্রেমলীলা।
এতে মূলত স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বিদ্যমান। কেবল বৈষ্ণব ধর্মানুসারীরা এগুলো রচনা করেননি, অসংখ্য মুসলমান কবিও রয়েছে যারা পরম আবেগে বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেন। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থে ১৬৪ জন বৈষ্ণব পদকর্তার নাম উল্লেখ করেছেন।
প্র. পদ বা পদাবলি বলতে কী বুঝায়?
উ. পদ বা পদাবলি বলতে প্রধানত শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলা নিয়ে গান করার জন্য রচিত প্রশংসাসূচক কবিতা বা বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্মের গূঢ় বিষয়কে নিয়ে রচিত সাহিত্যকে বুঝায়। মধ্যযুগে ‘পদাবলি’ সাহিত্যে ধর্মীয় ভাব প্রকাশের অন্যতম উপায় হিসেবে বিবেচিত হতো। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
হিন্দুদের উপনিষদে যে ব্রাহ্মকে রসস্বরূপ বলা হয়েছে এবং প্রিয়রূপে উপাসনা করতে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণকে সেই অনন্তরসের আধার আস্বাদন করার জন্য পদাবলি সাহিত্য রচিত হয়েছে। দ্বাদশ শতকে বাঙালি কবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় রচিত ‘গীতগোবিন্দম’ কাব্যে ‘পদাবলি’ শব্দটি প্রয়োগ করেন।
পদাবলির বৃহত্তম ও অধিক সমাদৃত সংকলন বৈষ্ণবদাস ওরফে গোকুলানন্দ সেনের ‘পদকল্পতরু’। এতে মোট ৩১০১টি পদ সংকলিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংকলিত ‘ক্ষণদাগীতচিন্তামণি’কে প্রাচীনতম পদাবলি সংকলন বলে ধরে নেওয়া হয়। উল্লেখ্য, শ্রীচৈতন্যেকে নিয়েও পদাবলি সাহিত্য রচিত হয়েছে।
প্র. বৈষ্ণব পদাবলি কী? (২৯তম বিসিএস লিখিত]
উ. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নিদর্শন বৈষ্ণব পদাবলি, যা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত। বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ক সৃষ্ট পদ বা পদাবলিই ‘বৈষ্ণব পদাবলি’। এতে কৃষ্ণ পরমাত্মার প্রতীক এবং রাধা জীবাত্মার প্রতীক।
বৈষ্ণবেরা ভগবান ও ভক্তের সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকে পরমাত্মা বা ভগবান এবং রাধাকে জীবাত্মা বা সৃষ্টির রূপক মনে করে তাদের বিচিত্র প্রেমলীলার মধ্যেই ধর্মীয় তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন। ফলে এক প্রাচীন গোপজাতির লোকগাঁথার নায়ক প্রেমিক কৃষ্ণ এবং মহাভারতের নায়ক অবতার কৃষ্ণ কালে কালে লোকস্মৃতিতে অভিন্ন হয়ে উঠেছে।
বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণব সমাজে ‘মহাজন পদাবলি’ এবং বৈষ্ণব পদকর্তাগণ ‘মহাজন’ নামে পরিচিত। বৈষ্ণবদের উপাস্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর প্রেমময় প্রকাশ ঘটেছে রাধার মাধ্যমে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
প্র. কবে বৈষ্ণব পদাবলির বিকাশ ঘটে?
উ. চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে এর রচনা শুরু হলেও শ্রী চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম মতবাদ প্রচার শুরু করলে ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়।
প্র. বৈষ্ণব পদাবলিতে কৃষ্ণ ও রাধা কে?
উ. বৈষ্ণব পদাবলিতে কৃষ্ণ পরমাত্মার এবং রাধা জীবাত্মার প্রতীক।
প্র. বৈষ্ণব পদাবলি কে সংকলন করেন?
উ. বাবা আউল মনোহর দাস। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে তিনি ‘পদসমুদ্র’ গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলি সংকলিত করেন। এতে প্রায় পনের হাজার কবিতা ছিল।
প্র. বৈষ্ণব পদাবলিতে কতটি রস আছে?
উ. ৫টি। যথা: শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এ পদাবলিতে বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণের ও তার প্রেয়সীভাবাপন্ন ভক্তদের যে মধুর সম্বন্ধ এবং এই প্রিয় সম্বন্ধজনিত পরস্পরের মধ্যে যে সম্ভোগ ভাব তার নাম মধুররস। বাংলা সাহিত্যে রস ৯ প্রকার। যথা: শৃঙ্গাররস, বীররস, রৌদ্ররস, বীভৎসরস, হাস্যরস, অদ্ভুতরস, করুণরস, ভয়ানকরস ও শান্তরস।
প্র. বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা কাকে বলা হয়?
উ. বাঙালি কবি জয়দেবকে (রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি) বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা বলা হয়। তিনি দ্বাদশ শতকে সংস্কৃত ভাষায় ‘গীতগোবিন্দম্’ নামে কাব্য রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এ কাব্যের মূল বিষয়। এটি তিনি ২৮৬টি শ্লোক এবং ২৪টি গীতের সমন্বয়ে ১২টি সর্গে রচনা করেন।
প্র. মৈথিল কোকিল’ কাকে বলা হয়?
উ. মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকে ‘মৈথিল কোকিল’ বলা হয়। তিনি পদাবলির আদি বৈষ্ণব কবি এবং পদসংগীত ধারার রূপকার। তাঁর উপাধি ‘কবি কণ্ঠহার’। তাকে ‘অভিনব জয়দেব’ নামে ডাকা হত। তিনি বাংলা সাহিত্যে একটি পক্তি না লিখেও বাংলায় স্মরণীয় কবি। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেন । মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
প্র. বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি কবি কে?
উ. চণ্ডীদাস।
প্র. বৈষ্ণব পদাবলির অন্যান্য কবি কে কে?
উ. জ্ঞানদাস: আনুমানিক ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে কবি জ্ঞানদাসের জন্ম। তিনি চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য ছিলেন। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদের মধ্যে যথেষ্ঠ সাদৃশ্য আছে । জ্ঞানদাস ছিলেন শিল্পী এবং চণ্ডীদাস ছিলেন সাধক।
মঙ্গলকাব্য
পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। পৌরাণিক, লৌকিক ও পৌরাণিক- লৌকিক সংমিশ্রিত দেব-দেবীর লীলামাহাত্ম্য, পূজা প্রচার ও ভক্তকাহিনী প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত সম্প্রদায়গত প্রচারধর্মী ও আখ্যানমূলক কাব্য হলো মঙ্গলকাব্য।
বিভিন্ন দেবদেবীর গুণগান এবং পূজা প্রতিষ্ঠার কাহিনী মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। তবে ‘মঙ্গল’ কথাটি থাকলেও ‘চৈতন্যমঙ্গল’, ‘গোবিন্দমঙ্গল’ প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়; এগুলো বৈষ্ণব সাহিত্যের অংশ। দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে, প্রায় ৬২ জন কবি মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন।
প্র. মঙ্গলকাব্য কী? [১৮তম বিসিএস লিখিত]
উ. বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যই মঙ্গলকাব্য। এটি রচনার মূল কারণ স্বপ্নদেবী কর্তৃক আদেশ লাভ। ‘মঙ্গল’ শব্দের অর্থ কল্যাণ। যে কাব্যে দেবতার আরাধনা বা মাহাত্ম্য-কীর্তন করা হয়; যে কাব্য শ্রবণ করলেও মঙ্গল হয় বা ঘরে রাখলেও মঙ্গল হয় অথবা এক মঙ্গলবার শুরু হতো এবং পরবর্তী মঙ্গলবার শেষ হতো, তাকেই বলা হয় মঙ্গলকাব্য।
মূলত, লৌকিক দেব-দেবী নিয়ে রচিত কাব্যই মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য: দেব-দেবীর গুণগান। এতে স্ত্রী দেবতাদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কাব্যগুলোর নামকরণ করা হত যে দেবতার পূজা প্রচারের জন্য কাব্যটি রচিত সে দেবতার নামানুসারে ।
প্র. মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ / বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন। (৩০/৩৫ তম বিসিএস লিখিত]
উ, বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যই মঙ্গলকাব্য। নিম্নে এর সাধারণ লক্ষণ / বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচিত হলো। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
- প্রায় সব কবি স্বপ্নে দেবতার নির্দেশ পেয়ে কাব্যরচনা করেছেন।
- প্রথমেই সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশের বন্দনা।
- কাব্যের অধিকাংশ ঘটনা সাধারণ নয়, অসাধারণ ।
- মঙ্গলকাব্যের উপাস্থাপিত নায়ক-নায়িকারা সকলেই শাপভ্রষ্ট দেবতা, শাপান্তে তারা স্বর্গে ফিরে যান।
- মর্ত্যে পূজা প্রচারের সময় দেবতাদের আচরণ মানুষের মতো ।
প্র. মঙ্গলকাব্য কত প্রকার ও কী কী?
উ. মঙ্গলকাব্য প্রধানত ২ প্রকার । যথা:
ক. পৌরাণিক শ্রেণি: ‘গৌরীমঙ্গল’, ‘ভবানীমঙ্গল’, ‘দুর্গামঙ্গল’, ‘অন্নদামঙ্গল’ ।
খ. লৌকিক শ্রেণি: ‘শিবমঙ্গল’, ‘মনসামঙ্গল’, ‘চণ্ডীমঙ্গল’, ‘সারদামঙ্গল’।
প্র. মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা কয়টি ও কী কী?
উ. মঙ্গলকাব্যে প্রধান শাখা ৩ টি । যথা :
ক. মনসামঙ্গল, খ. চণ্ডীমঙ্গল, গ. অন্নদামঙ্গল ।
প্র. মঙ্গলকাব্যের কয়টি অংশ থাকে?
উ. ৫টি। যথাঃ ক. বন্দনা, খ. আত্নপরিচয় ও গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ, গ. দেবখণ্ড, ঘ. মর্ত্যখণ্ড, ঙ. ফলশ্রুতি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
প্র. আদি মঙ্গলকাব্য কোনটি?
উ. মনসামঙ্গল। এটি মনসা দেবীর কাহিনী নিয়ে রচিত। এর অপর নাম ‘পদ্মপুরাণ’।
প্র. মঙ্গলকাব্যে কোন দুই দেবতার প্রাধান্য বেশী?
উ. মনসা ও চণ্ডী ।
প্র. মঙ্গলকাব্যের / মনসামঙ্গলের আদি কবি কে?
উ. কানাহরি দত্ত।
প্র. সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার অপর নাম কী?
উ. কেতকী ও পদ্মাবতী। অস্ট্রিক সমাজের লৌকিক ভয়ভীতি থেকেই এ দেবীর উদ্ভব। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
প্র. কোন দেবীকে নিয়ে মনসামঙ্গল রচিত?
উ. সাপের অধিষ্ঠাত্রী মনসা দেবীর কাহিনী নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্য রচিত। এ কাব্য মোট ৮ দিনে পরিবেশন করা হতো। শেষ দিনে পরিবেশন করা অংশকে বলা হয় ‘অষ্টামঙ্গল’। নিয়তির বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ এ কাব্যকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।
প্র. মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্তের পরিচয় দাও । [৩১/১৫তম বিসিএস]
উ. মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ কবি হলেন বিজয়গুপ্ত। বরিশাল জেলার ফতেহাবাদের ফুল্লশ্রী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সুস্পষ্ট সন- তারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। তাঁর রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগ্রন্থের একটি অংশের নাম ‘পদ্মপুরাণ’। শ্রাবণ মাসের মনসাপঞ্চমীতে স্বপ্নে দেবীর আদেশ পেয়ে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলে ১৪৯৪ সালে তিনি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
প্র. ‘বাইশা’ কী?
উ. মনসামঙ্গলের জনপ্রিয়তার জন্য বিভিন্ন কবির রচিত কাব্য থেকে বিভিন্ন অংশ সংকলিত করে যে পদসংকলন রচনা করা হয়েছিল তাই বাংলা সাহিত্যে বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা নামে পরিচিত।
প্র. ‘বারোমাসী’ বা ‘বারোমাস্যা’ কী?
উ. ‘বারোমাসী’ বা ‘বারোমাস্যা’ শব্দের অর্থ পুরো এক বছরের বিবরণ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লৌকিক কাহিনী বর্ণনায় নায়ক-নায়িকাদের বারো মাসের সুখ-দুঃখের বিবরণ প্রদানের রীতি দেখা যায়, একেই ‘বারোমাসী’ বা ‘বারোমাস্যা’ বলে।
প্র. ‘চৌতিশা’ কী?
উ. বিপন্ন নায়ক-নায়িকা চৌত্রিশ অক্ষরে ইষ্টদেবতার যে স্তব রচনা করে, তাকে বলে ‘চৌতিশা’। ব্যঞ্জনবর্ণ (‘ক’ থেকে ‘হ’) পদের আদিতে প্রয়োগ করে ‘চৌতিশা’ রচিত হতো। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
প্র. মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যান্য কবি / রচয়িতা কে কে?
উ. নারায়ণ দেব: কিশোরগঞ্জ জেলার বোর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পনের শতকের কবি বলে ধারণা করা হয়। তার রচিত গ্রন্থের নাম ‘পদ্মপুরাণ” ।
দ্বিজ বংশীদাস: মনসামঙ্গল কাব্য ধারার অন্যতম কবি দ্বিজ বংশীদাস বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা ক্ষেমানন্দ। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার পাতোয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কেতকাদাস তার উপাধি। তার কাব্যে মুকুন্দরাম ক্ষেমানন্দ: এ ধারার অন্যতম জনপ্রিয় কবি কেতকাদাস ও রামায়ণের কাহিনীর প্রভাব সুস্পষ্ট।
প্র. মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী আলোচনা কর?
উ. মনসামঙ্গলের কাহিনী: চম্পক নগরের অধীশ্বর বণিক চাঁদ সওদাগর। জগতপিতা শিবের মহাভক্ত। চাঁদ জগতপিতা শিবের থেকে মহাজ্ঞান লাভ করেছেন। মানুষের পূজা ব্যতীত। দেবত্ব অর্জন সম্ভব না হওয়াই মনসা চাঁদের থেকে পূজা চাইলেন।
শিব ছাড়া আর কাউকে পূজা করতে চাঁদ রাজি ছিলেন না। পরিশেষে পত্নী সনকার মনসার ঘটে হেঁতালদণ্ড দ্বারা আঘাত করেন। ফলে মনসা কৌশলে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করেন এবং ছয়পুত্রকে বিষ দিয়ে হত্যা করেন। তারপর সমুদ্রপথে চাঁদের বাণিজ্যতরী সপ্তডিঙা মধুকর ডুবিয়ে চাঁদকে সর্বস্বান্ত করেন।
চাঁদ কোনোক্রমে প্রাণরক্ষা করেন। মনসা পাঠালেন। অনিরুদ্ধ চাঁদের ঘরে জন্ম নেয় লখিন্দর রূপে, ছলনা করে স্বর্গের নর্তকদম্পতি অনিরুদ্ধ-ঊষাকে মর্ত্যে আর উজানী শহরে সাধুবণিকের ঘরে বেহুলারূপে ঊষা জন্ম নেয়।
বহুকাল পরে সহায় সম্বলহীন চাঁদ চম্পক নগরে পাগল বেশে আসে। অবশেষে পিতা পুত্রের মিলন ঘটল। বেহুলার সাথে লখিন্দরের বিবাহ স্থির হল। মনসা বৃদ্ধা বেশে এসে ছল করে বেহুলাকে শাপ দিল, ‘বিভা রাতে খাইবা ভাতার’। সাতালি পর্বতে লোহার বাসরঘর বানানো হল।
ছিদ্র পথে কালনাগিনী ঢুকে লখিন্দরকে দংশন করল। বেহুলা স্বামীর নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে পাড়ি দিল। বহু বিপদ মৃতদেহ অতিক্রম করে অবশেষে নেতো ধোবানির সাহায্যে দেবপুরে পৌছে নাচের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করল। তখন দেবতাদের আদেশে মনসা সব ফিরিয়ে দিল। বেঁচে উঠলো লখিন্দর, ভেসে উঠলো চৌদ্দ ডিঙা।
চাঁদ পাগলের মত ছুটে আসলো বেহুলার কাছে। এসে শুনলো যে তাকে মনসার পূজা করতে হবে। কিন্তু এ শর্ত চাঁদ প্রত্যাখান করলো। বেহুলা গিয়ে কেঁদে পড়ল চাঁদের পায়ে এবং চাঁদ বেহুলার অশ্রুর কাছে পরাজিত হল। চাঁদ হেলাভরে মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে একটি ফুল ছুড়ে দিল। মনসা এতেই খুশি। মর্ত্যবাসের মেয়াদ ফুরালে বেহুলা-লখিন্দর আবার ইন্দ্রসভায় স্থান পেল । আর পৃথিবীতে প্রচারিত হলো মনসার পূজা।
প্র. চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি কে?
উ. মানিক দত্ত । মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
প্র. চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি কে? [১৭তম বিসিএস লিখিত]
উ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তিনি ষোল শতকের কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যের নাম ‘শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল’ । তাঁকে দুঃখ বর্ণনার কবি হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর রচনার স্বীকৃতিস্বরূপ জমিদার রঘুনাথ রায় ‘কবিকঙ্কন’ উপাধি প্রদান করেন। মুকুন্দরামের জনপ্রিয় কাহিনীকাব্য ‘কালকেতু উপাখ্যান’।
প্র. কোন কাহিনী অবলম্বনে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত?
উ. চণ্ডীদেবীর কাহিনী। এটি দুই খণ্ডে বিভক্ত । প্রথমটি আখেটিক বা ব্যাধ কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী এবং দ্বিতীয়টি বণিক বা ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।
প্র. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কোন কবিকে ‘স্বভাব কবি’ বলা হয়?
উ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিজ মাধবকে ‘স্বভাব কবি’ বলা হয়। তাঁর রচিত কাব্যের নাম ‘সারদামঙ্গল’ (১৫৭৯)।
প্র. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ‘কালকেতু-ফুল্লরা’ খণ্ডের কাহিনী আলোচনা কর।
উ. কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী: দেবীর অনুরোধে ক্রমে শিব তার ভক্ত নীলাম্বরকে শাপ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। নীলাম্বর কালকেতু হয়ে জন্মনেন। কালকেতুর যৌবন বয়সে তার পিতা ধর্মকেতু ফুল্লরার সাথে বিবাহ দেন। তারা অতি দরিদ্র কিন্তু সুখী সংসার। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
এদিকে কালকেতুর শিকারে প্রায় নির্মূল কলিঙ্গের বনের পশুদের আবেদনে কাতর হয়ে দেবী স্বর্ণগোধিকা রূপে কালকেতুর শিকারে যাবার পথে প্রকট রূপ ধারণ করেন। কালকেতু শিকারে যাবার সময় অমঙ্গলজনক গোধিকা দেখার পর কোন শিকার না পেয়ে ক্রুব্ধ হয়ে গোধিকাটিকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে ঘরে নিয়ে আসেন।
কালকেতু গোধিকাকে ঘরে বেঁধে পত্নীর উদ্দেশ্যে হাটে রওনা হন। হাটে ফুল্লরার সাথে দেখা হলে তাকে গোধিকার ছাল ছাড়িয়ে শিক পোড়া করতে নির্দেশ দেন। ফুল্লরা ঘরে ফিরলে, দেবী এক সুন্দরী যুবতীর রূপে ফুল্লরাকে দেখা দিলেন। ফুল্লরার প্রশ্নের উত্তরে দেবী জানালেন যে, তার স্বামী ব্যাধ কালকেতু তাকে এখানে এনেছেন এবং তিনি এ গৃহেই কিছুদিন বসবাস করতে চান।
দেবীকে তাড়াতে ফুল্লরা নিজের বারমাসের দুঃখ কাহিনী বিবৃত করলেন, তবুও দেবী অটল। শেষ পর্যন্ত ফুল্লরা ছুটলেন হাটে, স্বামীর সন্ধানে। উভয়ে গৃহে ফেরার পর দেবীর অনুগ্রহে কালকেতু ধনী হয়ে পশু শিকার ত্যাগ করলেন। বনের পশুরাও নিশ্চিন্তে বসবাস করতে লাগল। দেবীর আশীর্বাদে ধনলাভ করে কালকেতু বন কেটে গুজরাট নগর পত্তন করেন।
গুজরাট নগরে নবাগতদের মধ্যে ভাঁড়দত্ত নামে ছিল এক প্রতারক । প্রথমে কালকেতু তাকে বিশ্বাস করলেও প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করায় তাকে তাড়িয়ে দেন। ভাঁড়দত্ত কলিঙ্গের রাজার কাছে গিয়ে তাকে কালকেতুর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। কলিঙ্গের সেনাপতি গুজরাট আক্রমণ করে কালকেতুকে বন্দী করেন। কিন্তু দেবীর কৃপায় কালকেতু মুক্তি পান এবং কাল পূর্ণ হলে ফুল্লরাসহ স্বর্গে ফিরে যান। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
প্র. অন্নদামঙ্গল ধারার প্রধান কবি কে?
উ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-১৭৬০)। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি এবং মঙ্গলযুগের শেষ কবি। তিনি নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ‘অন্নদামঙ্গল’ (১৭৫২-৫৩) কাব্য রচনা করেন। ‘সত্য পীরের পাঁচালী’ (১৭৩৭-৩৮) তাঁর রচিত অন্যতম গ্রন্থ। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে। ‘রায়গুণাকর’ ভারতচন্দ্রের উপাধি।
প্র. অন্নদামঙ্গল কাব্য কয়ভাগে বিভক্ত ও কার বন্দনা আছে?
উ. ৩টি খণ্ড । যথা:
১. শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল,
২. বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল,
৩. মানসিংহ-ভবানন্দ অন্নদামঙ্গল। (এ তিনটি খণ্ডেই দেবী অন্নদার বন্দনা আছে।] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
প্রঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যে কার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে?
উ. ধর্মঠাকুরের। ধর্মঠাকুর নামে কোনো এক পুরুষ দেবতার পূজা হিন্দু সমাজের নিচু স্তরের লোকদের বিশেষত ডোম সমাজে প্রচলিত ছিলো। ধর্মঠাকুর প্রধানত দাতা, নি:সন্তান নারীকে সন্তান দান করেন, অনাবৃষ্টি হলে ফসল দেন, কুষ্ঠ রোগীকে রোগ থেকে মুক্ত করেন। ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে যে কাব্যধারা রচিত হয় তাই ধর্মমঙ্গল কাব্য ।
প্র. ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?
উ. ময়ূরভট্ট। তাঁর রচিত কাব্যের নাম ‘হাকন্দপুরাণ’। এ কাব্যের আরও দুজন প্রখ্যাত কবি হলেন- রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরাম চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতকের মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠকবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম ‘শ্রী ধর্মমঙ্গল’ ।
প্র. ধর্মমঙ্গল কাব্য কয়টি পালায় বিভক্ত?
উ. দুটি পালা। যথা:
১. রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনী,
২. লাউসেনের কাহিনী।
প্র. কালিকামঙ্গল কাব্যে কার স্তুতি করা হয়েছে ?
উ. দেবী কালীর। এ কাব্য ‘বিদ্যাসুন্দর’ নামেও অভিহিত যা সাবিরিদ খান কর্তৃক রচিত। সাবিরিদ খান কর্তৃক রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ ‘রসুল বিজয়’। প্রকৃতপক্ষে এটি মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত নয় । দেবী কালীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। রাজকুমার ‘সুন্দর’ ও বীরসিংহের অপরূপা কন্যা ‘বিদ্যা’র গুপ্ত প্রণয়কাহিনী এ কাব্যের প্রধান উপজীব্য। এগার শতকের কাশ্মীরের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি বিলহন এর কাব্য ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ অবলম্বনে কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত।
প্র. কালিকামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?
উ. কবি কঙ্ক। সাবিরিদ খান ও রামপ্রসাদ সেন এ কাব্যের বিখ্যাত কবি। রামপ্রসাদ সেন শ্যামাসংগীত রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর উপাধি ‘কবিরঞ্জন’। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
প্র. শিবমঙ্গল কাব্য সম্পর্কে কি জান?
উ. কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবনে বৈদিক দেবতা রুদ্র শিবের রূপ ধারণ করে। বাঙালি হিন্দুদের জীবনে শিব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বাঙালির সুখ-দুঃখ ভরা সংসারের কথা স্থান পেয়েছে শিবমঙ্গল কাব্যে। পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান মিশ্রিত হয়ে শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্য রচিত।
√ শিবমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি রামকৃষ্ণ রায়।
√ এ ধারার প্রথম কাব্য দ্বিজ রতিদেব রচিত ‘মৃগলুব্ধ’ (১৬৭৪)।
√ এ ধারার শ্রেষ্ঠ কাহিনী রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য। তার রচিত কাব্যের নাম ‘শিবকীৰ্তন’। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
√ এ ধারার অন্যান্য কবি- দ্বিজ কালিদাস, দ্বিজ মণিরাম প্রমুখ।
 Sopner BCS Sopner BCS: We fuel your BCS dreams
Sopner BCS Sopner BCS: We fuel your BCS dreams

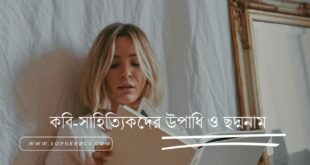

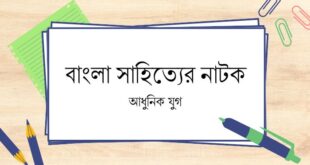
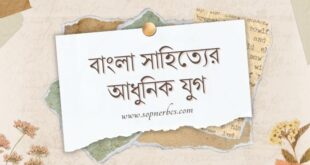
One comment
Pingback: বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান; যুগ সন্ধিক্ষণ - Sopner BCS