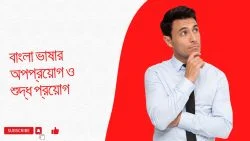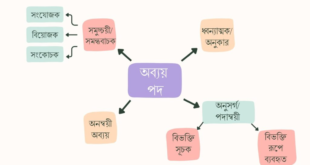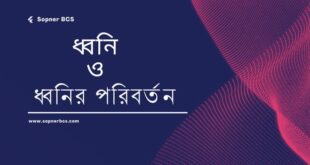সংজ্ঞাঃ বাংলা ভাষায় ব্যবহত যেসব শব্দ ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল প্রচলিত তাকে Proyog opoproyog অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ বলে। যেমনঃ অশ্রুজল।
অপপ্রয়োগের সংজ্ঞা ও অপপ্রওগ ঘটার কারণ
৩ টি কারণে ভাষার অপপ্রয়োগ ঘটে। যথাঃ
- উচ্চারণজনিত
- শব্দ গঠনজনিত
- অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত
উচ্চারণজনিতঃ আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণ-প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারা এবং শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি অসতর্কতায় বানানে অশুদ্ধি ঘটে। যেমনঃ অনাটন, উক্ত্যাক্ত ইত্যাদি।
শব্দ গঠনজনিতঃ শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে অপপ্রয়োগ ঘটে। যেমনঃ অপকর্ষতা, উৎকর্ষতা লিখিত হ বিশেষ্য-বিশেষণকে যথাযথ চিহ্নিত না করার কারণে।
অর্থগত বিভ্রান্তিজনিতঃ শব্দের অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে প্রয়োগ বিভ্রান্তি ঘটে থাকে এ বিভ্রান্তির ফলে বাক্যে ভুল শব্দ ব্যবহত হয়। যেমনঃ অবদান (কীর্তি), অবধান (মনোযোগ)।
অপপ্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দৃষ্টান্ত Watch video on Proyog Opoproyog
অত্র-তত্র-যত্রঃ “অত্র” শব্দের এখানে; তত্র শব্দের অর্থ “সেখানে”; এবং “যত্র” শব্দের অর্থ “যেখানে”। এই অর্থে ‘অত্র’ ব্যবহার অশুদ্ধ।
আকন্ঠ পর্যন্তঃ ‘আকন্ঠ’ দ্বারা কন্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। তাই এর সাথে ‘পর্যন্ত’ যোগ করা অশুদ্ধ।
অশ্রুজলঃ “চোখের জল” বোঝাতে “অশ্রুজল” শব্দটি ব্যবহার অপপ্রয়োগ। ‘অশ্রু শব্দ দ্বারাই চোখের জল বোঝায়। অন্তরীণঃ Interned বা বন্দি অর্তে “অন্তরিন” শব্দটি প্রচলিত। যেহুতু শব্দটি সংস্কৃত নয় কিংবা সংস্কৃত ব্যাকারণের নিওমে গঠিত নয়, তাই এ শব্দে দীর্ঘ- “ঈ” কার যেমন খাটে না, তেমনি মূর্ধন্য- “ণ” ও খাটে না।
অপেক্ষমাণ/অপেক্ষামানঃ ক্ষ অর্থাৎ ক-ইয়ে মূর্ধন্য-ষ আগে আছে বলে ণ-ত্ব ব্ধান অনুযায়ী “অপেক্ষমাণ” হবে, “অপেক্ষমান” নয়। “অপেক্ষমান” শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
ইদানীংকালঃ “ইদানীং বলতে বর্তমান কাল বোঝায়। অর্থাৎ ইদানীং শব্দের সাথে “কাল” যুক্ত। তাই “ইদানিংকাল” লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
আঙ্গিকঃ আঙ্গিকশব্দটির অর্থঃ অঙ্গ সম্বন্ধীয়। তাই “কলাকৌসল” অর্থে আঙ্গিক শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
উর্বরা শক্তি/ উর্বরতা শক্তিঃ “উর্বরা শক্তি” কথাটার ব্যহহার প্রায়ই দেখা যায়। ভূমিই “উর্বরা শক্তি” নয়। তাই “উর্বরা শক্তি’ত পরিবর্তে “উর্বরতা শক্তি” কথাওটার প্রয়োগই যাথার্থ।
দাহ্যশক্তি/দাহিকাশক্তিঃ দহন বা দাহন করার শক্তি বোঝাতে “দাহ্যশক্তি” লেখা ভুল প্রয়োগ। “দাহ্য” শব্দের অর্থঃ যা সহজে দগ্ধ হয় বা দহনযোগ্য। তাই “দাহ্যশক্তি’র” স্থলে লিখতে হবে “দাহিকা শক্তি”।
প্রথম/অতিপ্রথম/সর্বপ্রথমঃ ‘প্রথম’ শব্দের সাথে কোও তুলনামূলক শব্দ বা প্রত্যয় যুক্ত হয় না। এজন্য শব্দটি থেকে ‘অতি’ ও ‘সর্ব’ বাদ যাবে।
বাধ্যগতঃ “বাধ্য” বিশেষবাচক শব্দের অর্থ অনুগত। এক্ষেত্রে “গত” শব্দ যোগ করে “বাধ্যগত” ব্যবহার অশুদ্ধ।
সহসাঃ ‘সহসা’ শব্দের অর্থঃ হঠাৎ, অকস্মাৎ, অতর্কিত। তাই “শিগগির” অর্থে “সাহসা” শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
কৃচ্ছ্র/কৃচ্ছ্রতাঃ ‘কৃচ্ছ্র’ শব্দের অর্থঃ শারীরিক ক্লেশ, কষ্টসাধ্য বত। ‘কৃচ্ছ্র’ শব্দের সাথে ‘তা’ প্রত্যয়যোগে ‘কৃচ্ছ্রতা’ শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
পদক্ষেপঃ ‘পদক্ষেপ’ শব্দের অর্থঃ পদার্পণ বা পা ফেলা। ব্যবস্থা গ্রহণ অর্থে ‘পদক্ষেপ’ শব্দটির ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
প্রস্তাব/প্রস্তাবনাঃ ‘প্রস্তাব’ ও ‘প্রস্তাবনা’ শব্দের অর্থ যথাক্রমে ‘আলোচ্য বিষয়’ ও ‘ভূমিকা’ তাই ‘প্রস্তাব’ অর্থে ‘প্রস্তাবনা’ শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
খাঁটি গরুর দুধঃ কথাটি প্রচলিত থাকলেও তা অশুদ্ধ। শুদ্ধরুপ হলো- গরুর খাঁটি দুধ।
বৈদেহী/বিদেহীঃ বিদেহ’ শব্দ দ্বারা দেহশয়ন্য বা অশরীরী বোঝায়। ‘বিদেহ’ বিশেষণবাচক শব্দের সাথে ঈ-প্রত্যয়যোগে পূনরায় বিশেষণ করা হয়েছে। দুটো শব্দের ব্যবহারই অপপ্রয়োগ।
বিষাক্ত/বিষধরঃ ‘বিষাক্ত’ সাপ নয়, ‘বিষধর’ সাপ। ‘বিষাক্ত’ শব্দের অর্থঃ বিষমিশ্রিত, ‘বিষলিপ্ত’। বিষাক্তখাদ্য হতে পারে, ‘বিষাক্ত’ অশোভন- শব্দটি হবে ‘বিষধর’ সাপ।
মধুমাস/মধুফলঃ ‘মধুমাস’ শব্দের অর্থঃ চৈত্র মাস। বর্তমানে ‘জৈষ্ঠের আম, জাম, লিচু, ও অন্যান্য ফল কে বলা হচ্ছে ‘মধুফল’। এ প্রয়োগও শুদ্ধ নয়। মধুফল বলে প্রকৃতপক্ষে কোনো মাস নেই।
ফলশ্রুতিঃ ‘ফলশ্রুতি’ শব্দটি দ্বারা পূণ্যকর্ম করলে যে ফল হয় তার বিবরণ বা তা শোনা। ফল বা ফলাফল অর্থে ‘ফলশ্রুতি’ শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
ভাষাভাষীঃ ভাষা ব্যবহারকারী বোঝাতে ভাষীই যথেষ্ট। তবে “ভাষী” অর্থে আগে ভাষাভাষী শব্দটি ব্যবহার অশুদ্ধ।
পূর্বাহ্নেঃ “পূর্বাহ্ন” শব্দের অর্থঃ দিনের প্রথ ভাগ। অনেকেই পূর্বে বা আগে অর্থে ‘পূর্বাহ্ন” শব্দটির ব্যবহার করে, যা অপপ্র্যোগ।
সাম্প্রতিককালঃ ‘সাম্প্রতিক’ বা “সম্প্রতি” দ্বারা কাল বোঝায়। অর্থাৎ সাম্প্রতিক বা সম্প্রতি শব্দের সাথে ‘কাল’ যুক্ত। “সাম্প্রতিককাল” লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
সঠিকঃ ‘সঠিক’ শব্দটি দ্বারা বোঝায় কোনটি ঠিকের সাথে। আমরা ঠিক অর্থে সঠিক শব্দটির ব্যবহার করি। যদি “ঠিক” দ্বারা প্রকৃত অর্থ বোঝায় তাহলে ‘সঠিক’ শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।
তাপদাহঃ ‘তাপ’ শব্দটি অর্থঃ উষনতা, উত্তাপ বা দাহ। ‘তাপদাহ’ শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় ‘দাহদাহ’। তাপদাহ শব্দটির বহুল ব্যবহার থাকলেও শব্দটি শুদ্ধরুপ হলো ‘দাবদাহ’। যার অর্থ-দাবানলের তাপ।
কেবলমাত্র/শুধুমাত্রঃ যেখানে ‘কেবল’ লেখাই যথেষ্ট কিংবা ‘শুধু’ লিখলেই যেখানে চলে সেখানে ‘কেবলমাত্র’ বা ‘শুধুমাত্র’ লিখলে বাহুল্য দোষ ঘটে।
উপর্যুক্ত/উপরোক্তঃ ‘উপর’ সংস্কৃত শব্দ নয়, বাংলা শব্দ এবং এর সঙ্গে ‘উক্ত’ শব্দের সন্ধির ফলে ‘উপরোক্ত’ শব্দটির সৃষ্টির হয়েছে। কিন্তু ‘উক্ত’ (বচ+ত) শব্দ তৎসম শব্দ। একটি অতৎসম শব্দের সাথে একটি তৎসম শব্দের সহিত অবিধেয়। তাই ‘উপর’ শব্দের সাথে ‘উক্ত’ শব্দের সন্ধি না করে ‘উপরি’ (উপরি+উক্ত=উপর্যুক্ত) শব্দের সাথে ‘উক্ত’ শব্দের সন্ধি করাই উচিৎ।
উল্লেখ/উল্লিখিতঃ সংস্কৃতে (এবং বাংলায়ও) মূল ধাতুটি ‘লিখ” হলেও লেখা, লেখন, লেখক প্রভৃতি শব্দে ‘লে” আসে। কিন্তু লিখিত, অলিখিত। একই কারণে উল্লিখিত (উৎ+লেখ) হলেও উল্লেখিত নয়, উল্লিখিত লিখতে হবে। এ সম্পদ সতর্কতা প্রয়োজন।
জয়জয়কার/জয়জয়াকারঃ ‘জয়জয়াকার’ শব্দটি আঞ্চলিক; এর রীতিসিদ্ধ রুপ ‘জয়জয়কার’।
ঝরনা/ঝরণা/ঝর্ণাঃ যার জল ঝরে পড়ে তা-ই ঝরনা। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ নয় এটি। ঝরণা বা ঝর্ণা লেখা অনুচিত।
ফুটপাত/ ফুটপাতঃ ফুটপাত বা ফুটপাথ বাংলা শব নয়, ইংরেজি footpath এর প্রতিবর্ণ রুপ। একটি শব্দের অর্ধেক ইংরেজি ও অর্ধেক বাংলা স্বাভাবিক নয়। তবে ‘ফুটপাথ’ শব্দটি লেখা উচিৎ।
কৃতি/কৃতীঃ ‘কৃতি শব্দটি বিশেষ্য। এর অর্থ কাজ, সম্পাদিত কর্ম। অন্যদিকে ‘কৃতি শব্দটি বিশেষণ। এর অর্থ কৃতকার্য বা সফল হয়েছে এমন। তাই ‘কৃতি’ অর্থে “কৃতী” শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
প্রেক্ষিত/পরিক্ষিতঃ ‘প্রেক্ষিত’ শব্দটি এসেছে ‘প্রেক্ষণ’ থেকে, যার অর্থঃ দৃষ্টি। ফলে এ থেকে উদ্ভূত শব্দ ‘প্রেক্ষিত’ এর অর্থঃ দেখা হয়েছে এমন (অর্থাৎ দৃষ্ট)। তবে ‘প্রেক্ষাপট’ বা পটভূমি অর্থে ‘প্রেক্ষিত’ শব্দের ব্যবহার ভুল প্রয়োগ।
সমর্থক শব্দ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।
শব্দের বানানরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা অসতর্কতার ফলে শব্দের বানান বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এরকম কিছু দৃষ্টান্তঃ
| অশুদ্ধ শব্দ | শুদ্ধরুপ | অশুদ্ধ শব্দ | শুদ্ধরুপ |
| অসহ্যনীয় | অসহ্য | অধীনস্থ | অধীন |
| অস্তমান | অস্তায়মান | অগ্রসরমান | অগ্রসর |
| একত্রিত | একত্র | ঐক্যতা | ঐক্য/একতা |
| কেবলমাত্র | কেবল/মাত্র | কার্পণ্যতা | কার্পণ্য |
| চাপল্যতা | চাপল্য/চপলতা | নিরহংকারী | নিরহংকার |
| ইতিপূর্বে | ইতঃপূর্বে | সুকেশিনী | সুকেশা/সুকেশী |
| সৌন্দর্যতা | সৌন্দর্য | সুস্বাগত | স্বাগত |
ভাষায় ব্যবহিত শব্দের ঠিক অর্থে সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণেও প্রয়োগে বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এ ধরনের বিভ্রান্তির জন্য বাক্য ভুল শব্দ ব্যবহত হয়। দৃষ্টান্তস্বরুপঃ
| শব্দ | অর্থ | শব্দ | অর্থ |
| অবদান | কীর্তি | অবধান | মনোযোগ |
| অবিনীত | উদ্ধত | অভিনীত | যা অভিনয় করা হয়েছে |
| আশি | ৮০ সংখ্যা | আশী | সাপের বিষদাঁত |
| আসক্তি | অনুরাগ | আসত্তি | নৈকট্য |
| ঈশ | ঈশ্বর | ঈশ | লাঙল দন্ড |
| ঋতি | গতি | রীতি | পদ্ধতি |
| একদা | এককালে | একধা | এক প্রকারে |
| কাঁদা | কান্না | কাঁদা | কর্দম |
| খড় | বিচালি | খর | তীব্র |
| গিরিশ | মহাদেব | গিরীশ | হিমালয় |
| টিকা | তিলক | টীকা | সংক্ষীপ্ত ব্যাখ্যা |
| দিন | দিবস | দীন | দরিদ্র |
| বেদ | ধর্মগ্রন্থের নাম | বেধ | গভীরতা |
| ভিত | বুনিয়াদ | ভীত | শঙ্কিত |
| মিলন | সংযোগ | মীলন | চোখের বুঝিয়ে রাখা |
| যতি | বিরাম | যতী | সন্ন্যাসী |
| রাধা | রাধিকা | রাঁধা | রন্ধন |
| শুচি | পবিত্র | সূচি | তালিকা |
| স্বর্গ | দেবতার বাসস্থান | সর্গ | অধ্যায় |

বাক্যে শব্দের অশুদ্ধ ও শুদ্ধ প্রয়োগ
| অশুদ্ধ | একথা প্রমাণ হয়ে… | |
| শুদ্ধ | এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। | |
| অশুদ্ধ | খাঁটি গরুর দুধ স্বাস্ব্যের জন্য উপকারী । | |
| শুদ্ধ | গরুর খাঁটি দুধ স্বাস্ব্যের জন্য উপকারী । | |
| অশুদ্ধ | নদীর জল হ্রাস হয়েছে। | |
| শুদ্ধ | নদীর জল হ্রাস পেয়েছে। | |
| অশুদ্ধ | সকল শিক্ষার্থীগণ পাঠে মনোযোগী নয়। | |
| শুদ্ধ | সকল শিক্ষার্থী পাঠে মনোযোগী নয়। | |
| অশুদ্ধ | ছোট নাটকটি সবাইকে মুগ্ধ করলো। | |
| শুদ্ধ | নাটিকাটি সবাইকে মুগ্ধ করলো। | |
| অশুদ্ধ | দৈনতা প্রশাংসনীয় নয়। | |
| শুদ্ধ | দীনতা প্রশংসনীয় নয়। |
অধিক পরিমানে ভুল হওয়া বিষয় গুলোর মধ্যে Proyog Opoproyog চ্যাপ্টার টি অন্যতম। তাই বাংলা ভাষী হিসাবে আমাদের সবার উচিৎ বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।
 Sopner BCS Sopner BCS: We fuel your BCS dreams
Sopner BCS Sopner BCS: We fuel your BCS dreams