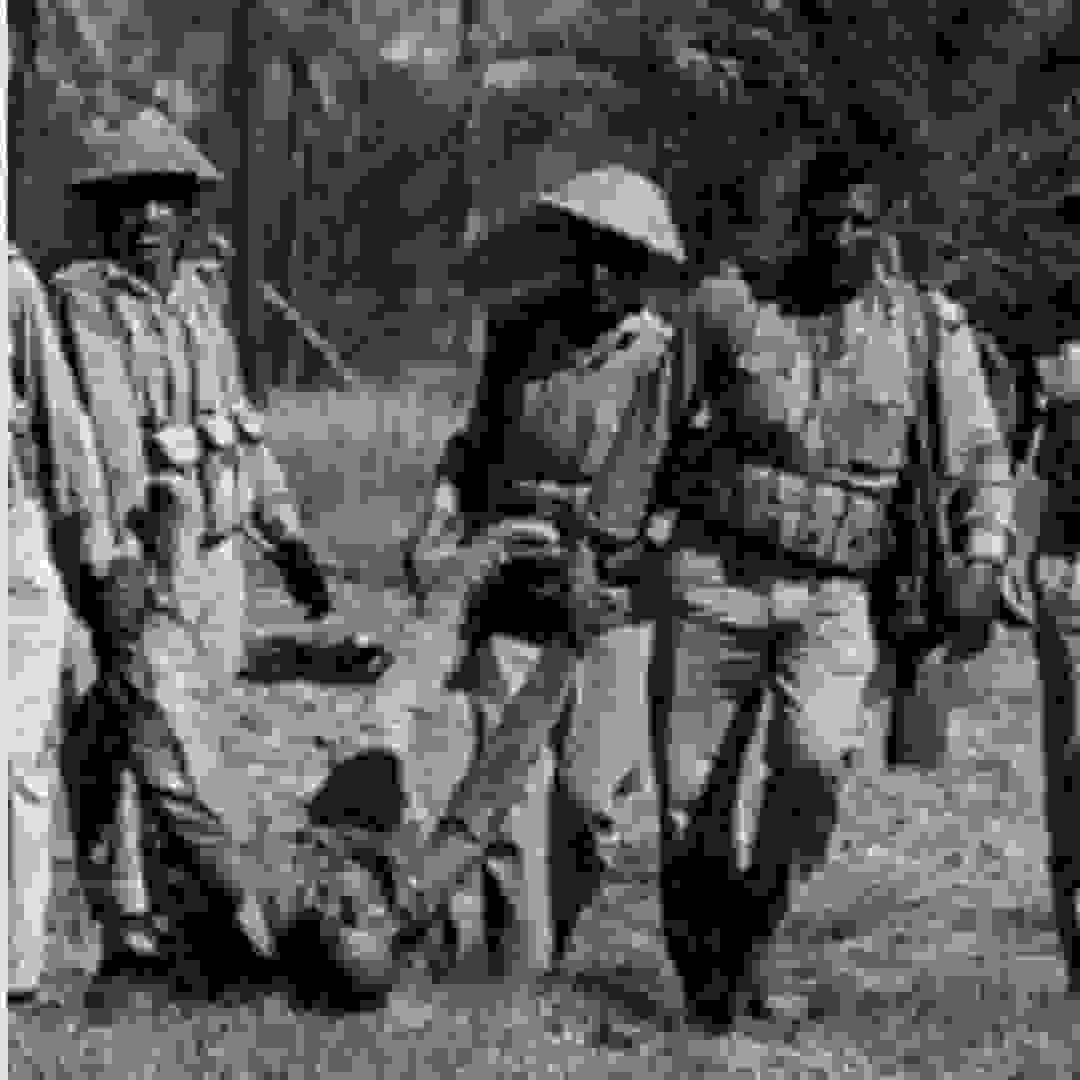বাংলাদেশের ইতিহাস; নবাবি শাসন ও কৃতিত্ব
বাংলাদেশের ইতিহাস সকল শিক্ষার্থী ও চাকুরি প্রত্যাশীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশ সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞানের আজকের আলোচনায় আমরা জানবো বাংলাদেশের ইতিহাস, নবাবি শাসন, নবাব বা সুবেদারদের অবদান ও কৃতিত্ব সম্পর্কে।
বাংলাদেশের ইতিহাস; নবাবি শাসন
ইসলাম খান, মীর জুমলা, শায়েস্তা খান, মুর্শিদকুলী খান, আলীবর্দী খান, এবং সিরাজউদদৌলা ছিলেন বাংলাদেশের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য শাসক এবং তাদের শাসনকাল থেকে প্রায় প্রতিটি চাকুরি পরিক্ষায় প্রশ্ন আসে। চলুন উনাদের শাসনকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য জানি।
ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩) বাংলাদেশের ইতিহাস
-
- বাংলায় নিযুক্ত প্রথম সুবেদার।
- ঢাকাকে সর্বপ্রথম রাজধানীর মর্যাদা দেন ।
- বারোভূঁইয়াদের দমন করেন।
- দোলাই খাল খনন করেন। [৩৬তম বিসিএস]
- নৌকাবাইচের প্রচলন করেন।
মীর জুমলা (১৬৬০-১৬৬৩)
-
- ১৬৬০ সালে বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তর করেন।
- ঢাকা গেইট (ঢা.বি. দোয়েল চত্বর সংলগ্ন) নির্মাণ করেন ।
- ১৬৬৩ সালে আসাম যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং ওসমানী উদ্যানের সামনে রক্ষিত কামানটি ব্যবহার করেন।
শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৭৮) (১৬৭৯-১৬৮৮)
-
- তাঁর সময়ে বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে ।
- চট্টগ্রাম থেকে মগ জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন এবং চট্টগ্রামের নামকরণ করে ইসলামাবাদ ।
- সাতগম্বুজ মসজিদ, ছোট কাটরা, লালবাগের কেল্লা নির্মাণ করেন ।
- রই উৎসাহে মীর মুরাদ ‘হোসেনী দালান’ নির্মাণ করেন। তারই সময়ে টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রি হতো।
মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-১৭২৭)
-
- বাংলার প্রথম নবাব ।
- ১৭১৭ সালে বাংলার স্থায়ী সুবেদার নিযুক্ত হন এবং রাজধানী ঢাকা হতে মকসুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) এ স্থানান্তর করেন ।
আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬) বাংলাদেশের ইতিহাস
-
- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব ।
- মারাঠাদের হাত থেকে বাংলার জনগণকে রক্ষা করেন ।
সিরাজউদদৌলা
-
- ১৭৫৬ সালে ইংরেজদের কাশিম বাজার দুর্গ দখল করেন।
- ১৭৫৬ সালে কলকাতা জয় করে নামকরণ করেন আলীনগর ।
- ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের সাথে আলীনগরের সন্ধি করেন।
- ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হলে বাংলায় মধ্যযুগের শাসনের অবসান ঘটে।
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ।
উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন
ইউরোপীয় বণিকদের আগমন চিত্র
| ক্রম. | দেশ | জাতি | বাংলায় যে নামে পরিচিত | আগমন সাল |
| প্রথম | পর্তুগাল | পর্তুগিজ | ফিরিঙ্গি | ১৫১৬ |
| দ্বিতীয় | নেদারল্যান্ডস | ডাচ | ওলন্দাজ | ১৬০২ |
| তৃতীয় | ইংল্যান্ড | ইংরেজ | ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি | ১৬০৮ |
| চতুর্থ | ডেনমার্ক | ডেনিশ | দিনেমার | ১৬১৬ |
| পঞ্চম | ফ্রান্স | ফরাসি | ফরাসি | ১৬৬৪ |
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন (১৭৫৭-১৮৫৮)
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলের সংস্কার কার্যক্রম
| সংস্কারক/ ইংরেজ শাসক | সংস্কার কার্যক্রম |
| লর্ড ক্লাইভ (১৭৬৫-১৭৬৭) | বাংলার প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর দ্বৈতশাসন কায়েম । ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। |
| ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৪) | দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন (১৭৭২)। পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত (১৭৭৩)। সাম্রাজ্যবাদী স্বত্ব বিলোপ নীতি (১৭৭৪)। |
| লর্ড কর্নওয়ালিশ (১৭৮৬-১৭৯৩) |
দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রবর্তন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)। সূর্যাস্ত আইন প্রবর্তন (১৭৯৩)। সতীদাহ প্রথা প্রবর্তন (১৭৯৩) জমিদারী প্রথার সূত্রপাত । |
| লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫) | অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তন । ব্রিটিশের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট । |
| লর্ড হেস্টিংস (১৮১৩-১৮২৩) | মারাঠা শক্তি ধ্বংস ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি । এই সময়েই রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। |
| লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক (১৮২৮-১৮৩৫) | কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮৩৫)। লর্ড ম্যাকলে কর্তৃক শিক্ষানীতি প্রণয়ন (১৮৩৫)। ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু (১৮৩৫)। সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইন (১৮২৯)। |
| লর্ড হেনরী হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-১৮৪৮) | ভারতবর্ষের রেল যোগাযোগ স্থাপন । গোলাপ সিংয়ের নিকট জম্মু ও কাশ্মীর বিক্রয়। শিশু হত্যা, নরবলি প্রথার বিলোপ । |
| লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬) | স্বত্ব বিলোপ নীতির প্রবর্তন । রেল লাইনের প্রচলন (১৮৫৩)। বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন (১৮৫৪, পাস-১৮৫৬) |
| লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬২) | কাগজী মুদ্রার প্রচলন (১৮৫৭)। সিপাহি বিপ্লবকালীন গভর্নর জেনারেল/ভাইসরয় । |
উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও সংস্কার আন্দোলন
ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন :
ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা লাভের পর সর্বপ্রথম বিদ্রোহ হলো ফকির বিদ্রোহ। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল; তাই ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন। বিদ্রোহী ফকির দলের নেতার নাম ছিল মজনু শাহ। আর সন্ন্যাসীদের নেতার নাম ছিল ভবানী পাঠক। তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি কুঠি, জমিদারদের কাচারি ও নায়েব- গোমস্তার বাড়ি ।
চাকমা বিদ্রোহ : বাংলাদেশের ইতিহাস
পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী চাকমা সম্প্রদায় ১৭৭৭ থেকে ১৭৮৭ পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে তা-ই চাকমা বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন চাকমা রাজা জোয়ান বকশ খান।
বারাসাত বিদ্রোহ : ১৮২৫ সালে ভারতের বারাসাত নগরীতে তিতুমীরের নেতৃত্বে ৮৩ হাজার কৃষকের অংশ গ্রহণে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তা-ই বারাসাত বিদ্রোহ। তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিছার আলী। ১৮৩১ সালে তিতুমীর কলকাতার অদূরে নারকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। ১৮৭১ সালে কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করা হয়। তিতুমীরসহ তার ৪০ সহচর এ আক্রমণে শহীদ হন । তিতুমীর প্রথম বাঙালি হিসেবে কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে শহিদ হন।
নীল বিদ্রোহ : বাংলাদেশের ইতিহাস
১৮৫৯ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত নীল চাষকে কেন্দ্র করে বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষে নীলকরদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সংঘটিত হয় তাকে নীল বিদ্রোহ বলে। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিগ্রো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে।
এই কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে নীল চাষকে কৃষকদের ‘ইচ্ছাধীন’ বলে ঘোষণা করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। পরবর্তীকালে নীলের বিকল্প কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে এদেশে নীল চাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।
ফরায়েজি আন্দোলন : বাংলাদেশের ইতিহাস
হাজি শরীয়ত উল্লাহ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এক ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। হাজি শরীয়ত উল্লাহর এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনকে ফরায়েজি আন্দোলন বলে।
ফরায়েজি শব্দটি আরবি ‘ফরজ’ (অবশ্য কর্তব্য) শব্দ থেকে এসেছে। যারা ফরজ পালন করে তারাই ফরায়েজি । হাজি শরীয়ত উল্লার মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার যোগ্যপুত্র মুহসিন উদ্দিন আহমেদ ওরফে দুদু মিয়া। ফরায়েজি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর। দুদু মিয়ার বিখ্যাত উক্তি- ‘জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থি’।
সিপাহি বিদ্রোহ : বাংলাদেশের ইতিহাস
পলাশীর যুদ্ধের একশ বছর পর ১৮৫৭ সালে ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে সিপাহিদের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাকে সিপাহি বিদ্রোহ (ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম) বলে।মঙ্গল পান্ডে সিপাহি বিদ্রোহের প্রথম শহিদ। তিনি ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন।
এই যুদ্ধে নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, অযোদ্ধার বেগম হজরত মহল, মৌলবি আহমাদ উল্লাসহ অনেকে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালে গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ক্যানিং। সিপাহি বিদ্রোহের ফলে কোম্পানির শাসনের অবসান হয় ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে।
বঙ্গভঙ্গ : বাংলাদেশের ইতিহাস
ভারতের বড়লাট, লড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বাংলা ভাগ করেন, যা ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। এর ফলে বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ।
এ প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয় ঢাকায় এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত হন ব্যামফিল্ড ফুলার। অপরপক্ষে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী হয় কলকাতা এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত হন এন্ড্র ফ্রেজার।
১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অভিষেক অনুষ্ঠানে রাজকীয় ঘোষণা বলে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের সময় ব্রিটিশ ভাইসরয় ছিল লর্ড হার্ডিঞ্জ। বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য রবীন্দ্রনাথ ‘রাখিবন্ধন’ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এবং আমার সোনার বাংলা গান রচনা করেন।
বঙ্গবঙ্গ রদ ঘোষণার প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার প্রতিবাদমুখর মুসলিম নেতৃবৃন্দকে শান্ত করার জন্য ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি বড় লাট হার্ডিঞ্জ ঢাকায় আসেন। তিনি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করেন। এই ওয়াদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
স্বদেশী আন্দোলন : বাংলাদেশের ইতিহাস
লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ৫ জুলাই সরকারিভাবে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৭ জুলাই খুলনার বাগেরহাটে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় প্রধানত বিলিতি পণ্যসামগ্রী বর্জন এবং ইংরেজদের সাথে সকল প্রকার অসহযোগিতা করার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করে।
যে ‘বয়কট’ প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে দুটি কর্মপন্থা ও ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিলিতি পণ্য বর্জনের মধ্য দিয়ে স্বদেশিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং বয়কট ছিল সামগ্রিকভাবে ইংরেজ শাসন ইংরেজদের সংস্পর্শ বর্জন।
একদিকে বয়কট ছিল নেতিবাচক ও অপরদিকে স্বদেশিকতা ছিল ইতিবাচক। আর এ দুটি কর্মপন্থা অবলম্বনে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার দিন থেকে বঙ্গভঙ্গের “বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে ‘স্বদেশী আন্দোলন’ নামে পরিচিত।
লক্ষ্ণৌ চুক্তি : বাংলাদেশের ইতিহাস
ব্রিটিশদের নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় একমত হলে লক্ষ্ণৌ শহরে ১৯১৬ সালে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তা-ই লক্ষ্ণৌ চুক্তি ।
অসহযোগ আন্দোলন : বাংলাদেশের ইতিহাস
ব্রিটিশ সরকার কুখ্যাত ‘রাউলাট আইন’ পাস করলে ভারতীয় জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই আইনে যে কোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল এ আইনের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের শান্তিপূর্ণ সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে ব্রিটিশ সরকার গুলি চালালে অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়।
জালিয়ানওয়ালাবাগ পাঞ্জাবের রাজধানী অমৃতসরের একটি উদ্যানের নাম। এর প্রতিবাদে কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধীজী হিংসাত্মক পথ বর্জন এবং সত্যাগ্রহ নীতিকে সামনে রেখে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন।
এ আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত সকল খেতাব ও সম্মানজনক পদবি প্রত্যাহার, বিদেশি পণ্য বয়কট, স্কুল- কলেজ, আদালত ইত্যাদি বর্জন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯ সালে এ আন্দোলনের প্রতি সম্মান জানিয়ে ব্রিটিশ প্রদত্ত ‘নাইট’ উপাধি বর্জন করেন। আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে।
এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানরা যেমন প্রথমবারের মতো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়, তেমনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় প্রথমবারের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামে।
খিলাফত আন্দোলন
ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য যে আন্দোলন করে তাকে খিলাফত আন্দোলন বলে। এই অন্দোলনে নেতৃত্ব দেন মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। খিলাফত আন্দোলন চলাকালীন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ‘অহিংস অসহযোগ আন্দোলন’ শুরু হয়।
গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনের প্রতিও তার সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এর ফলে খিলাফত আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯২৩ সালের ১৭ নভেম্বর তুরস্কের বিপ্লবী নেতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে ‘প্রজাতন্ত্র’ ঘোষণা এবং ‘খিলাফত’ তথা ‘তুরস্ক সালতানাতকে’ বাতিল ঘোষণা করেন। এর ফলে ভারতে খিলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা
১৯৩০ সালের মাস্টারদা সূর্য সেন তার দলবল নিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন ১৮ এপ্রিল অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ১৯৩২ সালের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের পাহাড়তলীর রেলওয়ে ক্লাব ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহিদ। ১৯৩৩ সালে সূর্য সেন আক্রমণ। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি সূর্য সেনকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং তাঁর মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।
দ্বিজাতিতত্ত্ব : বাংলাদেশের ইতিহাস
১৯৪০ সালের ২২ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জিন্নাহ মুসলমান ও হিন্দুদের জাতিসত্তা সম্পর্কে যে তাত্ত্বিক ভাবধারা বিশ্লেষণ করেন তা-ই দ্বিজাতিতত্ত্ব নামে পরিচিত। ভাষণে জিন্নাহ বলেন- ‘যে-কোনো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে মুসলমানরা একটা জাতি। তাই তাদের একটি পৃথক আবাসভূমি | প্রয়োজন, প্রয়োজন একটা ভূখণ্ডের এবং একটি রাষ্ট্রের।’ জিন্নাহ তার দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তি পেশ করেন-
ক. ভারত একটি দেশ নয়; বরং একটি উপমহাদেশ।
খ. যে ভিত্তিতে এ উপমহাদেশে হিন্দুরা একটি জাতি, সে ভিত্তিতে মুসলমানরাও একটি জাতি ।
গ. মুসলমানদের ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, নৈতিক বিধান, আচার- ব্যবহার, ইতিহাস-ঐতিহ্য হিন্দুদের থেকে ভিন্ন।
ঘ. হিন্দু-মুসলিম জনগণ অনুপ্রেরণা লাভ করে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে। অতএব আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞায় আমরা একটি জাতি।
তেভাগা আন্দোলন : বাংলাদেশের ইতিহাস
১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় কৃষকদের অধিকার আদায়ের জন্য যে আন্দোলন সংঘটিত হয়, তা-ই তেভাগা আন্দোলন। তেভাগা আন্দোলন বাংলার ১৯টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনটি তীব্র আকার ধারণ করেছিল দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, খুলনা, ময়মনসিংহ, যশোর এবং চবিবশ পরগনা জেলায়।
ভূমি মালিকরা ভাগচাষিদের এসব দাবি প্রত্যাখ্যান করে। তারা পুলিশ দিয়ে আন্দোলনকারীদের অনেককে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। কিন্তু জমিদারদের দমন-পীড়ন আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারেনি। অপ্রতিরোধ্য ভাগচাষিরা পরবর্তীকালে তাদের লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে জমিদারি প্রথা বিলোপের ক্ষেত্রে একটি নতুন স্লোগান যোগ করে।
বর্গাচাষিদের সমর্থনে পরিচালিত তেভাগা আন্দোলনে এ স্লোগানের সূত্রে খাজনার হার কমে আসার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। “মোট উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে কৃষক এবং এক ভাগ পাবে জমির মালিক”- এটিই ছিল এ অন্দোলনের মূল দাবি। ইলা মিত্র তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ছিল । তেভাগা আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাস নাঢ়াই ।
লাহোর প্রস্তাব : বাংলাদেশের ইতিহাস
১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে এ প্রস্তাবটি গৃহীত হয় বলে এটি ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত। উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।
মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন এ অধিবেশনের সভাপতি। একে ফজলুল হক ২৩ মার্চের অধিবেশনে তার রচিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়, কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকর হবে না, যদি এটি লাহোর প্রস্তাবে উত্থাপিত মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়।
হাজী মুহাম্মদ মুহসীন (১৭৩০-১৮৩২)
-
- বিশিষ্ট দানবীর, বাংলার হাতেম তাই বলে খ্যাত ।
- ১৮০৬ সালে মুহসিন ট্রাস্ট গঠন, হুগলী কলেজ ও হুগলী মাদ্রাসা এবং ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা।
রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৬)
-
- ১৮২২ সালে অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা।
- ১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ ।
- ১৮২৯ সালে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা।
- ১৮৩০ সালে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর কর্তৃক রাজা উপাধি গ্রহণ ।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)
১৮৪৯ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হন। বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রথা রোধকল্পে আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন ১৮৫৬ সালে।
নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)
-
- মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।
- ১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।
সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)
-
- সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা। লন্ডনে ব্রিটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা।
স্যার সৈয়দ আহমদ খান
-
- ১৮৭৭ সালে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা ।
- মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন।
- আলীগড় আন্দোলনের প্রবক্তা।
ব্রিটিশ সরকারের শাসন (১৮৫৮-১৯৪৭)
-
- বঙ্গভঙ্গ আইন পাস করা হয়- ১৯০৫ সালে
- ১৯০৫ সালের বঙ্গবঙ্গের সময় ভারতের ভাইসরয় ছিলেন- লর্ড কার্জন।
- বঙ্গবঙ্গ ব্যবস্থা রহিত করেন- লর্ড হার্ডিঞ্জ
- অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
- ‘পঞ্চাশের মন্বন্তর’ হয়েছিল- ১৯৪৩ সালে
- লাহোর প্রস্তাব ১৯৪০ এর মূল বিষয় ছিল- মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠন বা প্রতিষ্ঠা করার কথা
- ১৯৪৭ সালের সীমানা কমিশন যে নামে পরিচিত- র্যাডক্লিফ কমিশন।
কৃষ্টি ও সংস্কৃতি
-
- বিখ্যাত চিত্রকর্ম ‘তিন কন্যা’ এর চিত্রকর- কামরুল হাসান
- শিল্পী জয়নুল আবেদিনের সংগ্রহশালাটি- ময়মনসিংহে
- গম্ভীরা যে অঞ্চলের লোকসংগীত- চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- ‘কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়, তাই তো জাত ভিন্ন বলায়’ এ পঙ্ক্তিটির লেখক- লালন শাহ
- বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর অবস্থিত- সোনারগাঁ
- ‘একাত্তরের চিঠি’ গ্রন্থটির প্রকাশক- প্রথমা প্রকাশন
- বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জাদুঘর- বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর
- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকার যে এলাকায় অবস্থিত- সেগুনবাগিচা [বর্তমানে আগারগাঁও]
- বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরী নাচ যে অঞ্চলের- সিলেট
- সংস্কৃতি বলতে বোঝায়- প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত আচরণের সমষ্টি
- ‘সম্রাট আকবর বাংলা সন প্রবর্তন করেন- ১০/১১ মার্চ-১৫৮৪
- সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা সাল- ১৯৬১
- ছায়ানট কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকার নাম- বাংলাদেশের হৃদয় হতে
- ‘উদীচী’ শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা লাভ করে- ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর
- ‘উদীচী’ শব্দের অর্থ- উত্তর দিক
- ঐতিহাসিক গ্রন্থ ‘আইন-ই-আকবরী’-এর রচয়িতা- আবুল ফজল
- বাংলাদেশের বিশিষ্ট লালন গীতি গবেষক ড. আশরাফ সিদ্দিকী
- ময়মনসিংহ অঞ্চলের জনপ্রিয় লোকনাট্য- গীতিকা
- ‘দেওয়ানা মদীনা’ যার অসামান্য সৃষ্টি- মুনসুর বয়াতি
- ‘ঠাকুরমার ঝুলি’-এর লেখক- দক্ষিণাঞ্জন মিত্র মজুমদার
- বাংলাদেশের সুরসম্রাট বলা হয়- ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে
- ‘মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য’ গানটি গেয়েছেন- ভূপেন হাজারিকা
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ (বৃহত্তর রাজশাহী) অঞ্চলের গান- গম্ভীরা
- রংপুর অঞ্চলের গান- ভাওয়াইয়া
- ময়মনসিংহ অঞ্চলের গান- ভাটিয়ালী
- চট্টগ্রাম অঞ্চলের গান- ভাণ্ডারী
- নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার সময় পরিবেশিত গান- সারি
- বাংলাদেশের যে সংগীতজ্ঞ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন- ওস্তাদ আয়াত আলী খান
- বাংলা টপ্পা গানের প্রবর্তক- নিধু বাবু (প্রকৃত নাম রামনিধি গুপ্ত)
- ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের নাম- জারি
- রংপুর রাজশাহী অঞ্চলের নৃত্য— ঝুমুর
- খুলনা, ফরিদপুর ও যশোর অঞ্চলের বিখ্যাত নৃত্য- ধুপ নৃত্য
- ‘বল নৃত্য’ বাংলাদেশের যে অঞ্চলের- যশোর অঞ্চলের
- দেশের প্রথম আদিবাসী মেলা অনুষ্ঠিত হয়- কক্সবাজারে
- উপজাতীয় বর্ষবরণ উৎসবকে সামগ্রিকভাবে বলা হয়- বৈসাবি (বৈসুক, সাংগ্রাই ও বিঝুর সংক্ষিপ্ত রূপ)।
- জলকেলি যাদের উৎসব- রাখাইন
- লোকশিল্প জাদুঘরের বর্তমান নাম- জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর
- রাজশাহী ‘বরেন্দ্র জাদুঘর’ স্থাপিত হয়- ১৯১০ সালে
- ময়নামতির নিদর্শন- বৌদ্ধ ধর্মের (৭ম শতক)।
- দুর্ভিক্ষের উপর ‘ম্যাডোনা-৪৩’ ছবিটি এঁকেছেন- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
- মিনি বাংলাদেশ অবস্থিত- সোনারগাঁয়ে
- নড়াইলে অবস্থিত শিল্পী এসএম সুলতানের প্রতিষ্ঠিত চিত্রাঙ্কন প্রতিষ্ঠানের নাম- শিশুস্বর্গ
- ‘ধনধান্যে পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা’ গানটি রচনা করা হয়- ১৯০৫ সালে
- বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৮ সালে
- বিশ্ববরেণ্য সংগীতজ্ঞ আলি আকবর খাঁর পিতা- আলাউদ্দিন খাঁ
বোর্ড বই থেকে সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন
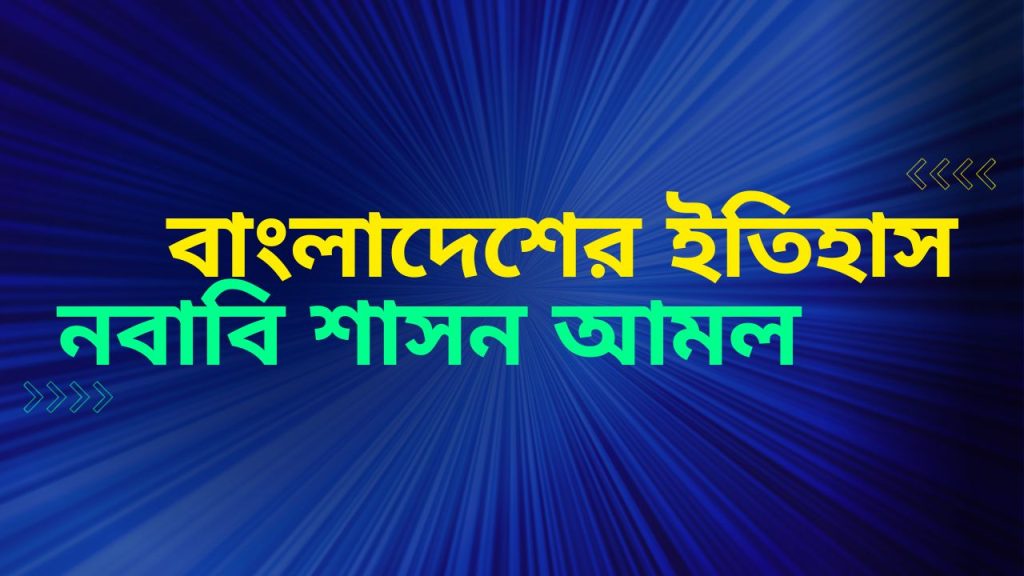
-
- প্রাচীন বাংলার জনপদ
- ইৎসিং কোন দেশের ভ্রমণকারী?- চীন দেশের
- সপ্তম শতকের পর বাংলায় কতটি জনপদ ছিল?- ৩টি
- মহাস্থানগড় অবস্থিত ছিল- বর্তমান বগুড়া শহর থেকে সাত মাইল দূরে
- হরিকেলের দক্ষিণে কোন জনপদ অবস্থিত ছিল?- তাম্রলিপ্ত জনপদ
- গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কী ছিল?- কর্ণসুবর্ণ
- স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কে? – শশাঙ্ক
- ‘অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থটির লেখক কে?- কৌটিল্য
- কার গ্রন্থে তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে গৌড়ের নাগরিকদের বিলাস ব্যাসনের পরিচয় পাওয়া যায়?- বাৎসায়নের গ্রন্থে
- কাদের আমলে গৌড়ের নাম-ডাক ছিল সবচেয়ে বেশি?- পাল রাজাদের আমলে
- প্রাচীন শিলালিপিতে কী নামে বঙ্গের দুটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়?- ‘বিক্রমপুর’ ও ‘নাব্য’ নামে
- কোথায় পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে?- বৈদিক সাহিত্য ও মহাভারতে।
- কার রাজত্বকালে প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্য স্বাধীন সত্তা হারায়?- মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে।
- শ্রীহট্ট কোন জেলার পূর্ব নাম? – সিলেট জেলার
- বরেন্দ্র কোন জনপদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিল?- পুণ্ড্রবর্ধন কোন জনপদকে জনপদ বলা যায় না?- বরেন্দ্র জনপদকে
- উৎকীর্ণ শিলালিপি ও সাহিত্যগ্রন্থ হতে মোট কতটি জনপদের কথা জানা যায়?- ১৬টি
- গৌড়ের উল্লেখ দেখা যায় সর্বপ্রথম কার গ্রন্থে?- পাণিনির
- গৌড়দেশের অনেক শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?- অর্থশাস্ত্রে
- কার শিলালিপি হতে প্রমাণিত হয় যে, সমুদ্র উপকূল হতে গৌড়দেশ খুব বেশি দূরে অবস্থিত ছিল না?- হর্ষবর্ধনের
- সর্বশেষ গৌড় বলতে কাকে বোঝাত?- সমগ্র বাংলাকে
- অতি প্রাচীন পুঁথি বঙ্গকে কোন জনপদের প্রতিবেশী বলা হয়েছে?- মগধ ও কলিঙ্গ
- পুণ্ড্রদের রাজ্যের রাজধানীর নাম কী?- পুণ্ড্রনগর
- পুণ্ড্রনগরের পরবর্তীকালে কী নাম হয়?- মহাস্থানগড়
- কার শাসনামলে প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্য স্বাধীন সত্তা হারায়?- সম্রাট অশোকের
- আধুনিক সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত জনপদের নাম কী?- হরিকেল
- চীনা ভ্রমণকারী ইৎসিংয়ের মতে হরিকেল ছিল কোথায়?- পূর্ব ভারতের শেষ সীমানায়
- চন্দ্রদ্বীপ কে অধিকার করেন?- ত্রৈলোক্যচন্দ্র
- কোন অঞ্চল নিয়ে সমতট গঠিত হয়েছিল?- কুমিল্লা-নোয়াখালী শালবন বিহারের অবস্থান প্রাচীন কোন জনপদে ছিল?- সমতট কুমিল্লা শহর থেকে বড় কামতার দূরত্ব কত?- ১২ মাইল
- সমতটের রাজধানী ছিল কোথায়?- বড় কামতা
- বড় কামতা নামক স্থানটি কত শতকে সমতটের রাজধানী ছিল?- সপ্তম
- বরেন্দ্র কোন বঙ্গের জনপদ ছিল?- উত্তর
- বরেন্দ্র কোন জনপদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিল?- পুণ্ড্রবর্ধনের।
- চন্দ্রদ্বীপ কোন জেলার পূর্বনাম?- বরিশাল
 Sopner BCS Sopner BCS: We fuel your BCS dreams
Sopner BCS Sopner BCS: We fuel your BCS dreams