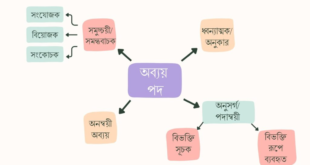ধ্বনি ও ধ্বনির পরিবর্তন নিয়ে লেখা এই নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে ধ্বনির সংজ্ঞা, ধ্বনি পরিবর্তন কত প্রকার, এবং ধ্বনির পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ও এর ভাষাগত প্রভাব। এই নিবন্ধটি ভাষাতত্ত্বের শিক্ষার্থী ও আগ্রহীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রিসোর্স হিসেবে কাজ করবে।
ধ্বনির পরিবর্তন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- ব্যাকরণে শুধু মানুষের মুখনিঃসৃত অর্থবোধক আওয়াজকেই ধ্বনি বলে ।
- ভাষার মূল উপাদান – ধ্বনি ।
ধ্বনি পরিবর্তন কত প্রকার
বাংলা ভাষার ধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যথা :
- স্বরধ্বনি
- ব্যঞ্জনধ্বনি
মৌলিক স্বরধ্বনি
- মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি । যথা : অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও ।
যৌগিক স্বরধ্বনি
- পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনি এক প্রয়াসে ও দ্রুত উচ্চারিত হয়ে যদি একটি যুক্ত ধ্বনিতে রূপ নেয়, তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা পঁচিশটি ।
- বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক ধ্বনি ও বর্ণ দুটি । যথা : i. ঐ (অ + ই) ii. ঔ (অ + উ)
- যৌগিক স্বরধ্বনিকে আরো যে নামে ডাকা হয়- দ্বিস্বর, সন্ধিস্বর, দ্বৈতস্বর, মিশ্র স্বরধ্বনি ও সংযুক্ত স্বরধ্বনি ।
পার্শ্বিক ধ্বনি- ‘ল’। জিহ্বার দু’পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে । একে আবার তরল ধ্বনিও বলা হয় ।
তাড়নজাত ধ্বনি
- ড়, ঢ় । জিহ্বার উল্টো পিঠের দ্বারা ওপরের দন্তমূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে উচ্চারিত হয় বলে এদেরকে তাড়নজাত ধ্বনি বলে ।
কম্পনজাত ধ্বনি
- ‘র’। জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে এবং দন্তমূলকে একাধিকবার আঘাত করে উচ্চারিত হয় বলে একে কম্পনজাত ধ্বনি বলে ।
অর্ধ-স্বরধ্বনি
- ই, উ, এ (য়) এবং ও । উদাহরণ: বই, ঘেউ, খায়, নাও ইত্যাদি ।
দীর্ঘস্বর
- যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণে সময় বেশি লাগে তাকে দীর্ঘ স্বরধ্বনি বলে । দীর্ঘ স্বরধ্বনি ৭টি । যথা : আ, ঈ, উ, এ, ঐ, ও, ঔ ।
হ্রস্ব স্বর
- যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণে সময় কম লাগে তাকে হ্রস্ব স্বরধ্বনি বলে। হ্রস্বস্বর ৪টি । যথা : অ, ই, উ, ঋ ।
উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ
| ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ | উচ্চারণ স্থান | উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম |
| ক, খ, গ, ঘ, ঙ | জিহ্বামূল | কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ |
| চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, শ, য, য় | অগ্রতালু | তালব্য বর্ণ |
| ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ষ, র, ড়, ঢ় | পশ্চাৎ দন্তমূল | মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ |
| ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স | অগ্র দন্তমূল | দন্ত্য বর্ণ |
| প, ফ, ব, ভ, ম | ওষ্ঠ | ওষ্ঠ্য বর্ণ |
ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকারভেদ
| উচ্চারণ স্থান | অঘোষ | ঘোষ | |||
| অল্প প্রাণ | মহাপ্রাণ | অল্প প্রাণ | মহাপ্রাণ | নাসিক্য | |
| কণ্ঠ | ক | খ | গ | ঘ | ঙ |
| তালু | চ | ছ | জ | ঝ | ঞ |
| মূর্ধা | ট | ঠ | ড | ঢ | ণ |
| দন্ত | ত | থ | দ | ধ | ন |
| ওষ্ঠ | প | ফ | ব | ভ | ম |
পরীক্ষায় আসার মতো আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- ক-ম পর্যন্ত ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনি বলা হয় । স্পর্শ ধ্বনির সংখ্যা- ২৫টি।
- বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনিকে বলে অঘোষ ধ্বনি । যেমন : ক + খ।
- বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিকে বলে ঘোষ ধ্বনি । যেমন : গ + ঘ । বর্গের ১ম + ৩য় + ৫ম ধ্বনি অর্থাৎ বিজোড় ধ্বনিকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে । যেমন : ক + গ + ঙ।
- বর্গের ২য় + ৪র্থ ধ্বনি অর্থাৎ জোড় ধ্বনিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে । যেমন : খ + ঘ ।
- উষ্ম ধ্বনি ৪টি । যথা : শ, ষ, স, হ ৷
- উচ্চারণের সময় মুখবিবরে কোথাও বাধা না পেয়ে কেবল ঘর্ষণপ্রাপ্ত এবং শিশ ধ্বনির সৃষ্টি করে বলে এদেরকে উষ্মধ্বনি বলে। এ ধ্বনিগুলোকে আবার উষ্ম বর্ণও বলা হয় ।
- • উষ্ম বর্ণের মধ্যে শ, ষ, স-কে শিষ ধ্বনি বলে এবং ‘হ’ হচ্ছে উষ্ম ঘোষধ্বনি ।
- এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে বলা হয় অক্ষর । যেমন : বন্ধন (বন্ + ধন্) শব্দে ২টি অক্ষর আছে ।
ধ্বনির পরিবর্তন
ধ্বনি পরিবর্তন এর সংজ্ঞা ও উদাহরণ
- উচ্চারণের সময় সহজীকরণের প্রবণতায় শব্দের মূল ধ্বনির যেসব পরিবর্তন ঘটে, তাকে ধ্বনির পরিবর্তন বলে । ১৮৭০ সালে খ্যাতনামা ধ্বনিবিজ্ঞানীরা একমত হয়ে বলেন যে, ভাষায় ধ্বনির পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক বা নিয়মিত ব্যাপার । যেমন : স্টেশন > ইস্টিশন, বাক্য > বাইক্য, মুলা > মুলো, শরীর > শরীল ।
ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

- উচ্চারণে দ্রুততা ও সহজতা ।
- উচ্চারণের অসাবধানতা ।
- মুখগহ্বরের প্রত্যঙ্গ, আড়ষ্টতা বা হীনতা ।
ধ্বনি পরিবর্তন এর নিয়ম
ভাষা পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, ধ্বনির পরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয় । নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :
স্বরাগম
উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্ত্যে স্বরধ্বনি এলে, তাকে স্বরাগম বলে । যেমন : স্পর্ধা > আস্পর্ধা, ফিল্ম > ফিলিম ও ট্যাক্স > ট্যাকসো ইত্যাদি ।
বিভিন্ন প্রকার স্বরাগমের সংজ্ঞা ও উদাহরণ
| নাম | সংজ্ঞা | উদাহরণ |
| আদি স্বরাগম | উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে আদি | স্বরাগম (Prothesis) বলে । | স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন, স্ত্রী > ইস্ত্রী, স্টেবল > আস্তাবল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা । |
| মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি | সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার ব্যঞ্জনধ্বনির জন্য সংযুক্ত মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে একে বলা হয়, মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি । | অ: রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, হর্ষ > হরষ ইত্যাদি | ই: প্রীতি > পিরীতি, ক্লিপ > কিলিপ, ফিল্ম > ফিলিম ইত্যাদি । উঃ মুক্তা > মুকুতা, তুর্ক > তুরুক, ভ্রূ > ভুরু ইত্যাদি । এঃ গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক, স্রেফ > সেরেফ ইত্যাদি । ও: শ্লোক > শোলোক, মুরগ > মুরোগ > মোরগ ইত্যাদি । |
| অন্ত্যস্বরাগম | কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে । এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম । | দিশ্ > দিশা, পোখত্ > পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি ইত্যাদি । |
স্বরসঙ্গতি (Vowel harmony)
একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে । যেমন: দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, মুলা > মুলো ইত্যাদি ।
বিভিন্ন প্রকার স্বরসঙ্গতির সংজ্ঞা ও উদাহরণ
| নাম | সংজ্ঞা | উদাহরণ |
| প্রগত (Progressive) | আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসঙ্গতি হয় | মুলা > মুলো, শিকা > শিকে, তুলা > তুলো, ফিতা > ফিতে, বিলাত > বিলেত ইত্যাদি । |
| পরাগত (Regressive) | অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে স্বরসঙ্গতি হয় । | আখো > আখুয়া > এখো, দেশি > পরাগত | দিশি, বেটি > বিটি, সন্ন্যাসী > সন্নিসি, গেল > গ্যালো ইত্যাদি । |
| মধ্যগত (Mutual) | আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত | | বিলাতি > বিলিতি, ভিখারি > ভিখিরি, জিলাপি > জিলিপি ইত্যাদি । |
| অন্যোন্য (Reciprocal) | আদ্য ও অন্ত্য ও অন্ত্য (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী) দুই স্বরই পরস্পরকে প্রভাবিত করে উভয়ই পরিবর্তিত হলে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি হয় । | মোজা > মুজো ইত্যাদি । |
| চলতি বাংলায় স্বরসঙ্গতি | চলিত বাংলায় কিছু স্বরসঙ্গতি পাওয়া যায় । | গিলা > গেলা, মিলামিশা > মেলামেশা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্ছে ইত্যাদি। পূর্বস্বর উ-কার হলে পরবর্তী স্বর ও- কার হয় । যেমন : মুড়া > মুড়ো, চুলা > চুলো ইত্যাদি । বিশেষ নিয়মে : উড়ুনি > উড়নি, এখনি > এখুনি হয় ইত্যাদি । |
সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ
উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয়। সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ। যেমন: বসতি > বসৃতি, জানালা > জান্লা ইত্যাদি ।
বিভিন্ন ধরনের সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপের সংজ্ঞা ও উদাহরণ
| নাম | সংজ্ঞা | উদাহরণ |
| আদিস্বরলোপ (Aphesis) | ধ্বনিলোপের ক্ষেত্রে শব্দের প্রথমের স্বরধ্বনির লোপ হলে তাকে আদিস্বর লোপ বলে। | অলাবু > পাবু > লাউ, উদ্ধার > উপার > ধার ইত্যাদি । |
| মধ্যস্বর লোপ (Syncope) | ধ্বনিলোপের ক্ষেত্রে শব্দের মধ্য স্বরধ্বনির লোপ হলে তাকে মধ্যস্বর লোপ বলে । | অগুরু >অগ্রু, সুবর্ণ স্বর্ণ ইত্যাদি । |
| অন্ত্যস্বর লোপ (Apocope) | ধ্বনিলোপের ক্ষেত্রে শব্দের শেষের স্বরধ্বনি উচ্চারণ থেকে বাদ গেলে তাকে অন্ত্যস্বর লোপ বলে । | আশা>আশ, আজি > আজ, চারি > চার, সন্ধ্যা > সঞঝা > সাঁঝ ইত্যাদি । |
| র-কার লোপ | আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয় । | তর্ক > তরু, করতে > কত্তে, মারল> মাল্ল, করলাম > কল্লাম ইত্যাদি । |
| হ-কার লোপ | আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয় । | পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাধু > সাউ, আরবি আল্লাহ > বাংলা আল্লা, ফারসি শাহ > বাংলা শা ইত্যাদি । |
সমীভবন (Assimilation )
শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করে, এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন । যেমন: জন্ম > জম্ম, কাঁদনা > কান্না ইত্যাদি ।
বিভিন্ন ধরনের সমীভবনের সংজ্ঞা ও উদাহরণ
| নাম | সংজ্ঞা | উদাহরণ |
| প্রগত (Progressive) সমীভবন | পূর্বধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে । অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, একে বলে প্রগত সমীভবন । | চক্র > চক, পদ > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগগ ইত্যাদি । |
| পরাগত (Regressive) সমীভবন | পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, একে বলে পরাগত সমীভবন। | তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ ইত্যাদি । |
| অন্যোন্য (Mutual) সমীভবন | যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয়, তখন তাকে বলে অন্যোন্য সমীভবন । | সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সক্ষ। সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা ইত্যাদি। |
অন্যান্য ধ্বনির পরিবর্তনের সংজ্ঞা ও উদাহরণ
| ধ্বনি বিপর্যয় | শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘতলে, তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে । | যেমন: ইংরেজি বাকস বাংলা বাস্ক, জাপানি রিক্সা > বাংলা রিসকা ইত্যাদি । অনুরূপ – পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল, ডেস্ক > ডেক্স, তলোয়ার > তরোয়াল ইত্যাদি |
| অপিনিহিতি (Apenthesis) | পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে, তাকে অপিনিহিতি বলে । | আজি > আইজ, সাধু > সাউধ, রাখিয়া > রাইখ্যা, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, চারি > চাইর, মারি ১ মাইর ইত্যাদি । |
| অসমীকরণ (Dissimilation) | একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তখন তাকে অসমীকরণ বলে । | ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ, পট + পট > পটাপট ইত্যাদি । |
| বিষমীভবন (Dissimilation ) | দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে । | শরীর > শরীল, লাল > নাল ইত্যাদি । |
| দ্বিত্ব ব্যঞ্জন (Long Consonant) বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বা | কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত শব্দের ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বা । | পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল ইত্যাদি । |
| ব্যঞ্জন বিকৃতি | শব্দ- মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়, একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। | কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি |
| ব্যঞ্জনচ্যুতি | পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায় । এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি । | বউদিদি > বউদি, বড় দাদা > বড়দা, বড়চাচা > বড়চা ইত্যাদি । |
| অন্তর্হতি | পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি বা বর্ণলোপ | | ফাল্গুন > ফাল্গুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা ইত্যাদি । |
| অভিশ্রুতি | বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অভিশ্রুতি। | করিয়া থেকে অপনিহিতির ফলে ‘কইরিয়া’ কিংবা বিপর্যয়ের ফলে ‘কইর’ থেকে অভিশ্রুতিজাত ‘করে’। এরুপ-শুনিয়া-শুনে, বলিয়া-বলে, হাটুয়া-হাউটা-হেটো, মাছুয়া-মেছো ইত্যাদি। |
| য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি | শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বি স্বর না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ ‘য়’ বা অন্তঃস্থ ‘ব’ উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়- শ্রুতি বা ব- শ্রুতি। | মা+আমার=মা য় আমার-মায়ামার। যা+আ=যা (ও) য়া= যাওয়া। এরুপঃ নাওয়া, খাওয়া,দেওয়া ইত্যাদি। |
 Sopner BCS Sopner BCS: We fuel your BCS dreams
Sopner BCS Sopner BCS: We fuel your BCS dreams