কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনীকে কেন্দ্র করে স্তুতিমূলক যে সাহিত্য রচিত হয়, তাই জীবনী সাহিত্য। মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্যগুলো বাংলা ভাষায় জীবনী সাহিত্য রচনার প্রথম প্রয়াস। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর তাঁর ভক্তরা চৈতন্যদেবের জীবনী নিয়ে সাহিত্য রচনা করা শুরু করেন। চৈতন্যদেবের জীবনচরিত পদ হিসেবে প্রথম সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। চৈতন্যের প্রথম জীবনীগ্রন্থ ‘মুরারি গুপ্তের কড়চা’, যা মুরারিগুপ্ত রচনা করেন। এ কাব্যের প্রকৃত নাম ‘শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃত’ ।
জীবনী সাহিত্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর
প্র. জীবনী সাহিত্য বলতে কি বুঝায়? (৩০তম বিসিএস লিখিত]
উ. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগে গতানুগতিক ধারায় জীবনী সাহিত্য এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনীকে কেন্দ্র করে স্তুতিমূলক যে সাহিত্য রচিত হয়, তাই জীবনী সাহিত্য। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর কতিপয় শিষ্যের জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি। চৈতন্য জীবনের কাহিনীতে কবিরা অলৌকিকতা আরোপ করেছেন। বৃন্দাবন দাস রচিত বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থ ‘চৈতন্য ভাগবত’।
অদ্বৈত আচার্য ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। অদ্বৈত আচার্য ও তার স্ত্রীকে নিয়ে হরকৃষ্ণ দাস সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন ‘বাল্যলীলাসূত্র’ (১৪৮৭)। তাকে নিয়ে প্রথম বাংলায় ‘অদ্বৈতপ্রকাশ’ নামে জীবনী রচনা করেন ঈশান নাগর ।
প্র. বাংলা সাহিত্যে একটি পঙক্তি না লিখেও কার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে?
উ. শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) ছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী এবং ষোড়শ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। পিতৃপ্রদত্ত নাম- বিশ্বম্ভর মিশ্র। ডাক নাম- নিমাই। চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম হলো ‘মানবপ্রেম ধর্ম’। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, ‘মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।’
প্র. শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থকে কি বলা হয়?
উ. কড়চা। এর অর্থ ডায়রি বা দিনলিপি
প্র. বাংলা সাহিত্যে কোন সময়কে চৈতন্য যুগ বলা হয়?
উ. ১৫০০-১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ।
প্র. শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার কে?
উ. কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তাঁর রচিত বাংলা ভাষায় সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থ ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ (১৬১৫)।
প্র. শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থগুলো কী কী?
- রচয়িতার নাম বৃন্দাবন দাস
- লোচন দাস
- কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুরারিগুপ্ত
গ্রন্থের নাম
- ‘চৈতন্য-ভাগবত’
- ‘চৈতন্যমঙ্গল’
- ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ (১৬১৫) ‘শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃত’
অন্যান্য জীবনী গ্রন্থ-
- রচয়িতার নাম সৈয়দ সুলতান ঈশান নাগর হরিচরণ দাস।
- গ্রন্থের নাম ‘নবী বংশ’, ‘শব-ই-মিরাজ’, ‘রসুল বিজয়’ ‘অদ্বৈতপ্রকাশ’
- ‘অদ্বৈতমঙ্গল’
প্র. বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের ভূমিকা কী? (৩৫ বিসিএস লিখিত]
উ. শ্রীচৈতন্যদেব বাংলা সাহিত্যে এক অমর প্রভাবক। বাংলা সাহিত্যে একটি অক্ষর না লিখেও সাহিত্যের এক বিশাল অংশজুড়ে তাঁর অবস্থান। তিনি এদেশে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিপর্যস্ত হিন্দু সমাজে যে নবচেতনার সঞ্চার করেছিলেন তাঁর অসীম প্রভাব ধর্মের সীমানা অতিক্রম করে তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্যে সম্প্রসারিত হয়ে তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।
সামন্তযুগের অনুদার মতাদর্শকে অস্বীকার করেই তিনি প্রচার করলেন জীবে দয়া, ঈশ্বরের ভক্তি এবং সকলের অধিকার। তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম বাংলা কবিতায় বৈষ্ণব দর্শনের প্রবেশ ঘটায়। এর মাধ্যমে বাংলা কাব্য দেব-দেবীর স্তুতিমূলক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে মানবধর্মের প্রশস্তিতে মেতে উঠে।
তাঁর অনুসারীরা একের পর এক রচনা করেন কালজয়ী জীবনী সাহিত্য। বৃন্দাবন দাস রচনা করলেন ‘চৈতন্য ভাগবত’। এটি বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচনা করলেন ‘চৈতন্যচরিতামৃত’। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী অবলম্বনে মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে জীবনী সাহিত্যের সূচনা হয় ।
নাথ সাহিত্য
দশম ও একাদশ শতক ছিল নাথ ধর্মের বিকাশের ঐতিহাসিক যুগ এবং নাথ ধর্মের এই শ্রেষ্ঠ যুগেই নাথ সাহিত্যের সূচনা । আদিনাথ শিব, মীননাথ, হাড়িপা ও কানুপা- এই চারজন সিদ্ধাচার্যের মাহাত্ম্যসূচক অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে নাথ সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।
প্র. নাথ সাহিত্য কী? (৩০তম বিসিএস লিখিত]
উ. বৌদ্ধ ধর্মমতের সাথে শৈবধর্ম মিশে ‘নাথধর্ম’ এর উদ্ভব। মধ্যযুগে শিব উপাসকদের নাথ ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে একশ্রেণির ধর্ম প্রচারকারী সাহিত্য।
প্র. নাথ সাহিত্য কত প্রকার ও কী কী?
উ. ২ প্রকার। যথা:
- মীননাথ ও তার শিষ্য গোরক্ষনাথের কাহিনী।
- রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস।
প্র. মুসলমান হয়েও কে নাথ সাহিত্য রচনা করেন / নাথ সাহিত্যের প্রধান কবি কে? (৩০তম বিসিএস লিখিত)
উ. শেখ ফয়জুল্লাহ। তিনি নাথ সাহিত্যের আদি কবি এবং তাঁর নাথ ধর্মবিষয়ের আখ্যানকাব্যের নাম ‘গোরক্ষ বিজয়’। এ কাব্যটি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আবিষ্কার করেন।
প্র. নাথ সাহিত্যের অন্যান্য কবি কারা?
উ. শুকুর মুহম্মদ (তাঁর লেখা নাথ সাহিত্য- ‘গোপীচাঁদের সন্ন্যাস’)। ভীমসেন রায়, শ্যামদাস সেন, ভবানী দাস।
মর্সিয়া সাহিত্য
মুসলমান সংস্কৃতির নানা বিষাদময় কাহিনী তথা শোকাবহ ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে মর্সিয়া সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে। এ সাহিত্য প্রধানত কারবালা প্রান্তরে নিহত ইমাম হোসেন ও অন্যান্য শহিদকে উপজীব্য করে লেখা। এদেশে এ সাহিত্যের প্রসার ঘটে বণিক, দরবেশ, কবি, পণ্ডিত প্রভৃতি আগমনকারী লোকদের অনুপ্রেরণায়। মুসলিম খলিফা ও শাসকদের বিজয় কাহিনীও এ শ্রেণিতে স্থান পেয়েছে।
প্র. মর্সিয়া সাহিত্য কী?
উ. মর্সিয়া অর্থ শোক প্রকাশ করা। এগুলো একধরনের শোককাব্য। ‘মর্সিয়া’ আরবি শব্দ। আরবি সাহিত্যে মর্সিয়ার নানা ধরনের শোকাবহ ঘটনা থেকে হলেও পরে তা কারবালা প্রান্তরে নিহত ইমাম হোসেন ও অন্যান্য শহিদকে উপজীব্য করে লেখা কবিতা ‘মর্সিয়া’ সাহিত্য নামে পরিচিত।
প্র. মর্সিয়া সাহিত্যের প্রথম কবি কে?
উ. শেখ ফয়জুল্লাহ। তাঁর রচিত কাব্য ‘জয়নবের চৌতিশা’ (১৫৭০) (কোনো কোনো রেফারেন্স গ্রন্থে এটির নাম ‘জয়নালের চৌতিশা হিসেবে উল্লেখ আছে। এটি কারবালার কাহিনীর একটি ছোট অংশ অবলম্বনে রচিত।
প্র. মর্সিয়া সাহিত্যে ‘জঙ্গনামা’ কে রচনা করেন?
উ. দৌলত উজির বাহরাম খান। ‘জঙ্গনামা’ (১৭২৩) কাব্য কারবালার বিষাদময় যুদ্ধ-বিগ্রহ এর বিষয়বস্তু।
প্র. মর্সিয়া সাহিত্যের অন্যান্য কবি কে কে?
উ. গরীবুল্লাহ, মুহম্মদ খান (তাঁর রচিত কাব্য ‘মক্তুল হোসেন’), হায়াৎ মামুদ, মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, রাধারমণ গোপ (হিন্দু কবি) ।
প্র. মর্সিয়া সাহিত্যের হিন্দু কবি কে?
উ. রাধারমণ গোপ। তাঁর রচিত কাব্য- ‘ইমামগনের কেচ্ছা’, ‘আফনামা” ।
প্র. যুদ্ধকাব্য কী?
উ. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর পরবর্তী বংশধরদের সাথে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধের কাহিনীভিত্তিক রচিত কাব্যই যুদ্ধকাব্য হিসেবে পরিচিত। মর্সিয়া সাহিত্যকেই যুদ্ধকাব্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। কয়েকটি যুদ্ধকাব্য: ‘জঙ্গনামা’ (দৌলত উজির বাহরাম খান), ‘রসুল বিজয়’ (শাহ বারিদ খান), ‘জয়কুম রাজার লড়াই’ (সৈয়দ সুলতান), ‘আমীর হামজা’ (ফকির গরীবুল্লাহ), ‘জয়নবের চৌতিশা (শেখ ফয়জুল্লাহ), ‘কাশিমের লড়াই (শেরবাজ) প্রভৃতি ।
লোকসাহিত্য
সংস্কৃতির যে সকল সাহিত্য গুণসম্পন্ন সৃষ্টি প্রধানত মৌখিক ধারা অনুসরণ করে অগ্রসর হয় তাকে লোকসাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ডাক ও খনার বচনকে লোকসাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবহমান কাল হতে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী, ছড়া, গান, কথা, গীতিকা, ধাঁধাঁ, গাঁথা প্রভৃতি লোকসাহিত্যের উপাদান ও নিদর্শন। লোকসাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যের শিকড়সন্ধানী সাহিত্য বলা হয়।
প্র. লোকসাহিত্য কী? (৩২তম বিসিএস লিখিত]
উ. সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কিন্তু অলিখিত সাহিত্য যা গাথাঁকাহিনী, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদির সামষ্টিক রূপ।
3) ঝগড়া ধ নিয়তি
সাধারণত কোনো সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। বাংলার অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী লোকসাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখেছেন। এদের একটি বড় অংশ লোক-কবি, যাদের সাধারণত ‘বয়াতি’ বলা হয়। এ সাহিত্যে ভালবাসা, আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।
প্র. লোকসাহিত্যের আদিরূপ কী কী?
উ. ছড়া, প্রবাদ/প্রবচন ও ধাঁধা ।
প্র. লোকসাহিত্য সংগ্রহে কে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন?
উ. ড. দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি পল্লী অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে প্রাচীন বাংলার পুঁথি ও লোককথা সংগ্রহ করেন এবং তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ (১৯২৩) ও ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১৯২৬)। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬)। রেভারেন্ড লাল বিহারী ‘Folk Tales of Bengal (১৮৮৩) বইটি রচনা করে লোকসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।
√ ড. সুনীল কুমার দে ‘প্রবাদ সংগ্রহ’ ও ড. মযহারুল ইসলাম ‘কবি পাগলা কানাই’ নামে গ্রন্থ রচনা করে লোকসাহিত্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখেন।
লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গবেষক হলেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, ড. আশরাফ সিদ্দিকী।
প্র. বিখ্যাত লোকগীতি ‘হারামনি’র সম্পাদক কে?
উ. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন। এটি ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত।
প্র. গীতিকা কী?
উ. গীতিকা বলতে আখ্যানমূলক লোকগীতিকে বুঝায়, যাকে ইংরেজিতে বলে Ballad. প্রাচীন যুগে ইউরোপের দেশ গুলোতে নাচের সাথে এই ধরণের গীত গাওয়া হতো। এই সব কবিতায় মূলত কোন দৈব দুর্ঘটনা বা কোন বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনীর বর্ণনা থাকে।
প্র. বাংলাদেশে কত ধরনের গীতিকা সাহিত্য প্রচলিত ও কী কী?
উ. তিন ধরনের। যথা:
ক. নাথ গীতিকা
খ. মৈমনসিংহ গীতিকা
গ. পূর্ববঙ্গ গীতিকা।
প্র. গীতিকাগুলো কে সংগ্রহ করেন?
উ. ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় চন্দ্রকুমার দে গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন ।
প্র. নাথ গীতিকা কী?
উ. একটিমাত্র ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হয় নাথ গীতিকা। রাজা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র মায়ের নির্দেশে যৌবনে দুই নব পরিণীতা বধুকে রেখে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। যার কাহিনীকে ঘিরেই রচিত ‘নাথ গীতিকা’ ।
প্র. মানিকচন্দ্র রাজার গান’ কে প্রকাশ করেন?
উ. ১৮৭৮ সালে ভাষাবিজ্ঞানী জর্জ গ্রিয়ারসন রংপুরের কৃষকদের কাছ থেকে ‘ময়নামতি গোপীচন্দ্রের পুঁথি’ সংগ্রহ করে ‘মানিকচন্দ্র রাজার গান’ নামে প্রকাশ করেন যা পরবর্তীতে ১৯২২ সালে ‘কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়’ থেকে ‘গোপীচন্দ্রের গান’ নামে প্রকাশিত হয়।
প্র. নাথ গীতিকাগুলো কী কী?
- ময়নামতির গান – ভবানীদাস শুকুর মহম্মদ
- গোপীচাঁদের সন্ন্যাস
প্র. ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ কী? [২০তম বিসিএস লিখিত]
উ. বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে যে কবিতা বা গীত বা পালাগান প্রচলিত ছিল বা প্রচারিত হতো, সেগুলোকে ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ বলে। এ গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত পালাসমূহে কথিত শিক্ষিত সমাজের বাইরে সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে।
এতে সামসময়িক কালের হিন্দুদের কুপ্রথা ও মুসলমানদের ফতোয়াবাজি থেকে মুক্ত সমাজব্যবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে পালাগুলোর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত পরিলক্ষিত হয়নি এবং প্রাচীন হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির চরম মিথষ্ক্রিয়া লক্ষ করা যায়।
প্র. ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ কে সম্পাদনা করেন?
উ. বর্তমান নেত্রকোনা জেলার আইথর/রাঘবপুর গ্রামের অধিবাসী চন্দ্রকুমার দে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাটি অঞ্চল থেকে গীতিকা সংগ্রহ করেন, যা দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত হয়।
পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে এটি চারখণ্ডে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এ চারখণ্ডের প্রথম খণ্ড ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ নামে পরিচিত। এটি বিশ্বের ২৩টি ভাষায় অনূদিত হয়।
প্র. ‘ঠাকুরমার ঝুলি’, ‘ঠাকুরদাদার ঝুলি’ কে সম্পাদনা করেন?
উ. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।
প্র. ‘মৈমনসিংহ গীতিকাগুলো কী কী? [৩২/২০তম বিসিএস লিখিত]
উ. ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ মোট ১০টি।
- মহুয়া (চরিত্র: নদের চাঁদ, মহুয়া)
- মলুয়া (চরিত্র: মলুয়া, চাঁদ বিনোদ)
- কমলা
- দস্যু কেনারামের পালা; রচয়িতা দ্বিজ কানাই
- চন্দ্রাবতী; দ্বিজ ঈশান
- মনসুর বয়াতি
- দেওয়ানা মদিনা (চরিত্র: আলাল, দুলাল, মদিনা) মনসুর
- দেওয়ান ভাবনা
- কাজলরেখা চন্দ্রাবতী
- কঙ্ক ও লীলা রূপবতী
প্র. পূর্ববঙ্গ গীতিকা কে সম্পাদনা করেন?
নয়ানচাঁদ ঘোষ দমোদর,রঘুসুত, নয়াচাঁদ ঘোষ অজ্ঞাত
উ. ড. দীনেশচন্দ্র সেন নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে এগুলো সংগ্রহ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে ১৯২৬ সালে ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’ নামে তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। এতে পালাগানের সংখ্যা ৫০ এর অধিক।
প্র. পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলো কী কী?
উ. নিজাম ডাকাতের পালা, কাফন চোরা, কমল সওদাগর, চৌধুরীর লড়াই, কাঞ্চন মালা, আয়না বিবি, ভেলুয়া, কমলা রাণীর গান ইত্যাদি।
প্র. ডাক ও খনার বচন কোন যুগের সৃষ্টি?
উ. ডাক ও খনার বচন প্রাচীন যুগের সৃষ্টি হলেও মধ্যযুগের শুরুতে এগুলো সমৃদ্ধি লাভ করে। একসময়ে বাংলাদেশে ডাক ও খনার বচন ব্যাপক প্রচলিত ছিল।
ডাক: বৌদ্ধদের জ্ঞানপুরুষ ডাক। এ বৌদ্ধ সমাজেই ডাকের বচনের উৎপত্তি হয়েছিল। কৃষক ও কৃষাণীরা এগুলো মুখস্থ রাখতেন। ডাক কোন একক ব্যক্তি বিশেষের নাম নাও হতে পারে। হয়ত একাধিক ব্যক্তি কালক্রমে বিশেষ জ্ঞানের যে পদগুলো রচনা করেছেন তাকেই ডাকের বচন বলা হয়।
ডাকের বচন ‘ডাকের কথা’ বা ‘ডাক পুরুষের কথা’ নামেও পরিচিত। এতে জ্যোতিষ, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও মানব চরিত্রের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন: ঘরে আখা বাইরে রাঁধে, অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে।
খনা খনার বচন প্রধানত কৃষিভিত্তিক। খনার বচন ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বৌদ্ধ সমাজে যেমন ডাকের বচনের উৎপত্তি হয়েছিল, তেমনি হিন্দু সমাজে খনার বচনের সৃষ্টি হয়েছিল। এ বচনগুলি জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এক বিদুষী বাঙালি নারীর রচিত বলে ধরে নেয়া হয়। খনার বচনগুলির মাধ্যমে প্রধানত কৃষি, আবহাওয়া, সমাজের পরিচয় সম্পর্কে বহুবিধ ধারণা পাওয়া যায়। যেমন:
- কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস। একে তো নাচুনি বুড়ি, তার উপর ঢোলের বাড়ি।
- কলা রুয়ে না কেটো পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত ।
- আলো হাওয়া বেধ না, রোগ ভোগে মরো না।
- উনা ভাতে দুনা বল, অতি ভাতে রসাতল ।
- আউশ ধানে চাষ লাগে তিন মাস ।
- আগে খাবে মায়ে, তবে পাবে পোয়ে।
- গাছে গাছে আগুন জ্বলে, বৃষ্টি হবে খনায় বলে ।
- তেলা মাথায় ঢালো তেল, শুকনো মাথায় ভাঙ্গ বেল । দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।
- ভাত দেবার মুরোদ নাই, কিল দেবার গোসাঁই ।
প্র. লোককথা বা লোককাহিনী কাকে বলে?
উ. গদ্যের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণিত হলে তাকে লোককথা বা লোককাহিনী বলে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Folklore. কাহিনীগুলো কাব্যে রূপায়িত হলে ‘গীতিকা’ এবং গদ্যে বর্ণিত হলে তা ‘কথা’ নামে পরিচয় লাভ করে। ড. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতে, লোককথা ৩ প্রকার। যথা:
১. রূপকথা
২. উপকথা
৩. ব্রতকথা ।
প্র. রূপকথা কী?
উ. নানা অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য কাহিনী নিয়ে রচিত সাহিত্যই রূপকথা। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Fairy Tales. বাস্তব রাজ্যের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো অপুত্রক রাজার দৈব বলে পুত্রলাভ, ভাগ্যান্বেষণে রাজপুত্রের দেশান্তরে গমন এবং বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন, পরিণামে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজ্য লাভ করে সুখে কালযাপন- এ ধরণের কাহিনী কাঠামোর উপর রূপকথার ভিত্তি ও প্রকাশ।
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের সংগৃহীত রূপকথার নাম ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ (১৯০৭), ‘ঠাকুরদাদার ঝুলি’ (১৯০৯), ঠানদিদির থলে’ (১৯০৯), ‘দাদামশায়ের থলে’ (১৯১৩), ‘কিশোরদের মন’ (১৯৩৩)। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর রূপকথা সংগ্রহের নাম ‘টুনটুনির বই” (১৯৬৪)।
প্র. উপকথা কী?
উ. পশু-পাখির কাহিনী অবলম্বনে রচিত সাহিত্যই উপকথা। কৌতুক সৃষ্টি এবং নীতি প্রচারের জন্য এগুলোর সৃষ্টি। এতে মানব চরিত্রের মতই পশুপাখির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। ইংরেজির ঈশপের গল্প, সংস্কৃতে পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ এরূপ নীতিকথার উৎকৃষ্ট উদাহরণ
প্র. ব্রতকথা কী?
উ. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েলি ব্রতের সাথে সম্পর্কিত কাহিনী অবলম্বনে ব্রতকথা নামে এক ধরনের লোককথার বিকাশ ঘটেছে। এসব কাহিনীতে যে ধর্মবোধের কথা বলা হয়েছে তাতে মেয়েদের জাগতিক কল্যাণ নিহিত।
প্র. চন্দ্রকুমার দে এবং দীনেশচন্দ্র সেনের নাম কেন লোকসাহিত্য প্রেমীদের হৃদয়ে চিরদিন জেগে থাকবে? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
উ. চন্দ্রকুমার দে লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ও লেখক। অর্থনৈতিক দৈন্যদশার কারণে বেশিদুর পড়ালেখা করতে পারেননি। ফলে নামমাত্র বেতনে চাকরি করেছেন বিভিন্ন জায়গায়। অবশেষে কেদারনাথের মাধ্যমে চন্দ্রকুমার দে দীনেশচন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করেন এবং মাসিক সত্তর টাকা বেতনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্য সংগ্রাহক পদে নিযুক্ত হন।
চন্দ্রকুমার দে সারা বাংলা ঘুরে ঘুরে লোকসাহিত্য ও লোকসংগীত সংগ্রহ শুরু করেন। পরবর্তীতে এসকল সংগৃহীত সাহিত্য দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ ও ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’ নামে প্রকাশিত হয়। ফলে চন্দ্রকুমার দেশ-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেন এবং লোকসাহিত্য প্রেমীর হৃদয়ে জায়গা করে নেন ।
রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন একাধারে ছিলেন শিক্ষাবিদ, গবেষক, লোকসাহিত্য বিশারদ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার। দেশের সংস্কৃতির প্রতি গভীর মমতা থাকার কারণে তিনি দেশের অতীতের সাহিত্যকে জনসমক্ষে আনতে ব্যাপক প্রয়াস চালান।
বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য বিলুপ্তি থেকে উদ্ধার এবং এ সাহিত্য বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সম্পাদনায় সংগৃহীত এ লোকসাহিত্য ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ ও ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’ নামে প্রকাশিত হয়। ফলে তিনি সর্বত্র প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন এবং লোকসাহিত্যপ্রেমীর হৃদয়ে জায়গা করে নেন।

অনুবাদ সাহিত্য
মধ্যযুগের কবিরা পয়ার ছন্দে অনুবাদ সাহিত্য ভাবানুবাদ করতেন। পুরাণ কাহিনীগুলো মূলত অনুবাদ করতেন হিন্দু কবিরা আর মুসলমান কবিরা ফারসি, হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন। কবিরা মূল কাহিনী ঠিক রেখে মাঝে মাঝে নিজেদের মনের কথা অন্তর্ভুক্ত করেছেন ।
√ অনুবাদ সাহিত্যে হিন্দু লেখকদের দ্বারা অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম ‘সাহিত্যের কথা’।মুসলমান সাহিত্যিকদের অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম ‘রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান’।
প্র. মহাভারত কে রচনা করেন?
উ. মহাভারত রচিত হয় প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে, যা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ১৮ খণ্ডে ও ৮৫০০০টি শ্লোকে বেদব্যাস ‘সংস্কৃত’ ভাষায় এটি রচনা করেন। পাণ্ডব বংশের পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে কুরু বংশের ১০০ ভাইয়ের যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস রচনা করেন মহাভারত। বেদ বাক্য ব্যাখ্যা করার কারণে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ এর নাম হয় ‘বেদব্যাস’। বেদব্যাস হিমালয়ের এক পবিত্র গুহায় তপস্যা করে এবং মহাভারতে ঘটনা সমূহ গণেশ এর মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেন।
প্র. মহাভারত প্রথম বাংলায় কে অনুবাদ করেন?
উ. ষোল শতকের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর । তিনি সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি চট্টগ্রামের পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায়
এটি অনুবাদ করেন বলে এর নামকরণ করেন ‘পরাগলী মহাভারত’।
প্র. মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
উ. সতের শতকের কবি দেব বংশের কাশীরাম দাস। তার অনূদিত বিখ্যাত পক্তি-
‘মহাভারতের কথা অমৃত সমান, কাশীরাম দাস ভনে শোনে পুণ্যবান।
প্র. ‘ছুটিখানী মহাভারত’ কে রচনা করেন?
উ. পরাগল খার পুত্র ছুটি খানের (প্রকৃত নাম- নসরত খান) নির্দেশে শ্রীকর নন্দী এটি রচনা করেন। তিনি শুধু অশ্বমেধপর্ব অনুবাদ করেন।
প্র. রামায়ণ কে রচনা করেন?
উ. সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ। এটি রচনা করেন বাল্মীকি। তাঁর মূল নাম- দস্যু রত্নাকর। এটি ২৪ হাজার শ্লোকে রচিত এবং ৭টি কাণ্ডে বিভক্ত (আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড)। শ্লোকগুলো ৩২ অক্ষরযুক্ত ‘অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত। এ কাব্যের উপজীব্য হল বিষ্ণুর অবতার রামের জীবনকাহিনী। ‘বল্মীক’ শব্দের অর্থ উইপোকা । দস্যু রত্নাকর উইপোকার ঢিবির উপর বসে রাম নামের তপস্যা করতেন বলে তার নাম হয় বাল্মীকি
 Sopner BCS Sopner BCS: We fuel your BCS dreams
Sopner BCS Sopner BCS: We fuel your BCS dreams
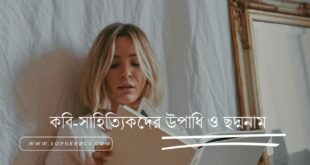

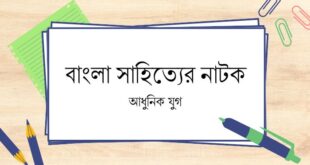
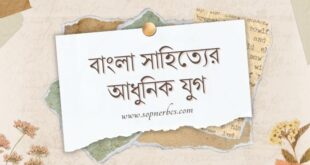
One comment
Pingback: বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ - Sopner BCS