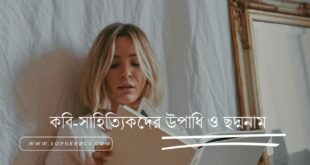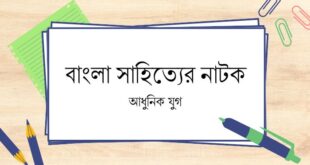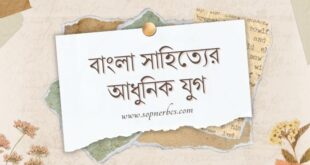রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা হয় মধ্যযুগে। মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে আসে সুলতানি আমলে । মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দু- বৌদ্ধ রচিত বাংলা সাহিত্যে দেব-দেবীই প্রধান ছিল, মানুষ ছিল অপ্রধান। মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যেই প্রথম মানুষ প্রাধান্য পায়। ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত অনুবাদমূলক প্রণয় কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মতো মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।
প্র. বাংলা ভাষার প্রথম মুসলিম কবি কে? [২৫তম বিসিএস লিখিত]
উ. শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম বাঙালি মুসলিম কবি ।
প্র. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য কী? (৩০তম বিসিএস লিখিত]
উ. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলিম কবিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে ও পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের প্রথম পদার্পণ ঘটে। এ কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো-
১. প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক ও দেবতাকেন্দ্রিক রচনা ছেড়ে এ কাব্যে প্রথমবারের মতো মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় ।
২. এগুলো বাংলা ও বাঙালির কাহিনী নয়, বাইরে থেকে অনুবাদ করে নিজস্ব রূপ দেয়া ৷
৩. গতানুগতিক সাহিত্যধারার বাইরে নতুন ভাবনা-চিন্তা ও রস- মাধুর্যের পরিচয় প্রকাশ করা ।
প্র. ‘ইউসুফ জোলেখা’ কে অনুবাদ করেন? [২৭/১৫/১০তম বিসিএস লিখিত]
উ. শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি আবদুর রহমান জামি রচিত ‘ইউসুফ ওয়া জুলায়খা’ (তথ্যসূত্র: ওয়াকিল আহমেদ সম্পাদিত ‘বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান’ এর অন্তর্ভুক্ত ‘ইউসুফ জোলেখা’, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সম্মান শ্রেণির পাঠ্য) থেকে বাংলায় ‘ইউসুফ-জোলেখা’ নামে অনুবাদ করেন। এ কাব্যের পটভূমি ইরান।
প্র. ‘ইউসুফ জোলেখা’ কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ ৷
উ. ইউসুফ জোলেখা কাব্যের কাহিনী: তৈমুর বাদশা দেবধর্ম আরাধনা করে এক কন্যারত্ন লাভ করেন; তাঁর নাম রাখেন জোলেখা। অসামান্য সুন্দরী জোলেখা পর পর তিনবার দেবতুল্য এক যুবাপুরুষকে স্বপ্নে দেখে তাঁর প্রণয়াসক্ত হন। স্বপ্নের নির্দেশমতো জোলেখা মিশরের বাদশা আজিজ মিশিরকে বরমাল্য দিলেন, কিন্তু আজিজ মিশির স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না। দৈববাণী কর্তৃক আশ্বাস লাভ করে জোলেখা ভারাক্রান্ত মন ও প্রণয়পীড়িত দেহ নিয়ে কালযাপন করেন।
এদিকে কেনান দেশের ইয়াকুব নবীর পুত্র ইউসুফের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের ও কৃতিত্বের ঈর্ষাকাতর বৈমাত্রেয় দশ ভ্রাতা তাকে কুপে নিক্ষেপ করে হত্যা করার চেষ্টা করে। মনিরু নামের মিশরবাসী এক বণিক ইউসুফকে কুপ থেকে উদ্ধার করে মিশরে নিয়ে যান এবং দাসরূপে বিক্রয় করেন।
জোলেখার অনুরোধক্রমে আজিজ মিশির তাকে খরিদ করেন এবং নিজ অন্তঃপুরে নিয়ে যান। ইউসুফের রূপমুগ্ধ জোলেখা প্রেমনিবেদন করলে ইউসুফ ধর্ম ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। জোলেখা ছলাকলার মাধ্যমে, প্রতারণা করে ইউসুফ কে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
কিন্তু কিছুকাল পরে আজিজ মিশিরের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে ইউসুফ মুক্তিলাভ করেন এবং মিশরের মন্ত্রিত্ব পান। ইউসুফ দক্ষতার সাথে রাজকার্য পালন করেন এবং আজিজ মিশিরির মৃত্যুর পর তিনি মিশরের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হন। জোলেখা বৃদ্ধ ও অন্ধত্বপ্রাপ্ত হয়ে ইউসুফের সাক্ষাতের আশায় পথে অপেক্ষা করতে থাকেন।
পরিশেষে একদিন সাক্ষাৎ হয় এবং ইউসুফের প্রার্থনায় জোলেখা হৃতযৌবন ও রূপসৌন্দর্য ফিরে পান। উভয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। যথাসময়ে তারা দুটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। পরপর কয়েক বছর অনাবৃষ্টির কারনে চতুর্দিকে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। ইয়াকুব নবী উপায়ন্ত না দেখে স্বীয় পুত্রদের খাদ্যের সন্ধানে মিশরে প্রেরণ করেন।
ইউসুফ তার বিশ্বাসঘাতক ভাইদের চিনতে, কিন্তু তিনি পরিচয় গোপন রেখে তাদের মেহমানদারী করেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যশস্য দিয়ে দেন। পরবর্তীতে মিশরে আসলে ইউসুফ ইবনে আমিনকে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। যখন ইবনে আমিনের সাথে ইউসুফের সাক্ষাৎ হয় ইউসুফ তাকে তার পরিচয় দেন এবং চুরির অপবাদ দিয়ে তাকে নিজের কাছে রেখে দেন।
পিতা ইয়াকুবকে মিশরে আনার জন্য দ্রুতগামী অশ্ব দিয়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের বিদায় করেন। ইয়াকুব মিশরে উপনীত হলে ত্রিশ বছর পর পিতা-পুত্রের মিলন হয়। ইউসুফ ভ্রাতাদের রাজকীয় দায়িত্ব দিয়ে মিশরে রাজত্ব করেন। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
কিছুকাল পরে বারহা-তনয়ার সাথে জ্যেষ্ঠপুত্রের এবং নৃপতি আমির-তনয়ার সাথে কনিষ্ঠপুত্রের বিবাহ দেন। অতঃপর ইউসুফ দিগ্বিজয়ে বের হন। অনেক রাজ্য জয়ের পর মৃগয়ার সময়ে মধুপুরের রাজা শাহাবাগের রূপবতী কন্যা বিভুপ্রভার সাক্ষাৎ পান।
বিভুপ্রভার ঈন্সিত পাত্র ইবন আমিনের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। অপুত্রক শাহাবাল জামাতাকে মধুপুর রাজ্য দান করেন। ইউসুফ মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুকাল পরে ইবনে আমিন ও বিধুপ্রিয়া মিশরে এসে বৃদ্ধ ইয়াকুবের পদবন্দনা করেন। জোলেখা বিধুপ্রভাকে বরণ করেন। ইউসুফ মিশরে এবং ইবন আমিন মধুপুরে সুখে রাজত্ব করেন।
প্র. ‘লায়লী-মজনু’ কে অনুবাদ করেন? ২৭/১৫/১০তম বিসিএস লিখিত]
উ. দৌলত উজির বাহরাম খান। তিনি পারসিয়ান কবি জামির ‘লায়লা ওয়া মজনুন’ থেকে এটি বাংলায় অনুবাদ করেন। এর উৎস আরবি লোকগাঁথা ।
প্র. ‘লায়লী-মজনু’ কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ।
উ. লায়লী-মজনু কাব্যের কাহিনী:
আরবের এক ধনী আমির বহু দয়া-ধ্যান করে একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন, তার নাম রাখেন কয়েস। পাঠশালায় পড়ার সময়ে মালিক নন্দিনী লায়লীর সাথে কয়েসের সাক্ষাৎ ও প্রণয় হয়। লায়লীর মাতা লায়লীর প্রেমকথা জানতে পেরে কুল-কলঙ্কের ভয়ে তার পাঠ বন্ধ করে দেন এবং কয়েসের সাথে সাক্ষাৎ বা পত্রবিনিময় যাতে করতে না পারে, তার জন্য সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
বন্দিনী লায়লী কেবল বিলাপ ও অশ্রুপাত করে কালযাপন করে। এদিকে প্রেমপরাহত কয়েস ভিখারী ছদ্মবেশে লায়লীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে ধরা পড়ে এবং মালিকের নির্দেশে প্রহরী কর্তৃক নির্যাতিত হয়। লায়লীর প্রেমধ্যান করে কয়েস গৃহত্যাগ করে নজদ বনে আশ্রয় নেয়। প্রেমোন্মত্ত ও বিরহকাতর কয়েসের নাম হয় ‘মজনু’ (পাগল)। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
আমির অনেক চেষ্টা করেও মজনুর মতি-পরিবর্তন করতে পারেননি।
গৃহে আত্মীয় পরিজন-সহচরী পরিবেষ্টিত থেকেও লায়লী বিরহ-যন্ত্রনা ভোগ করে ও অনবরত বিলাপ করে। আমিরের অনুরোধে মালিক লায়লী মজনুর বিবাহে সম্মত হন, কিন্তু বিবাহবাসরে মজনুর প্রেমোন্মত্ততার কারণে তা ভেঙ্গে যায়।
মজনু নজদ বনে ফিরে যায় এবং লায়লীর প্রেমধ্যান করতে করতে ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হয়। আমির আশা ভঙ্গে ও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেন। ইবন সালামের পুত্রের সাথে লায়লীর বিবাহ হয় বটে কিন্তু বাসরঘরে লায়লীর পদাঘাত পেয়ে নববর গৃহত্যাগ করে চলে যায়। এক বৃদ্ধার মুখে মজনু লায়লীর বিবাহ-সংবাদ পেয়ে ‘হৃদয়শোণিতে’ তাকে পত্র দেয়। লায়লীর পত্র পেয়ে মজনু শান্ত হয়।
নয়ফল-রাজ মৃগয়ায় এসে মজনুকে উদ্ধার করেন এবং মালিককে যুদ্ধে পরাভূত করে লায়লীকে বন্দি করেন। পরে লায়লীর রূপে তিনি নিজেই বন্দি হন এবং বিষপান করিয়ে মজনুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন।
সাকির প্রমাদে বিষমিশ্রিত পানীয় পান করে নয়ফল-রাজ মৃত্যুবরণ করেন।লায়লী তার পিতার মাধ্যমে উদ্ধার হন। কিছুদিন পর লায়লী তার পিতামাতার সাথে নিজেই উটে চড়ে শ্যামদেশে যায় এবং মজনুর সাথে মিলিত হয়। মজনু লায়লীকে ফেরত পাঠায়। লায়লী মজনুর বিরহে মৃত্যু বরণ করেন এবং মজনুও লায়লীর শোকে বিলাপ করতে থাকে।
আরাকান রাজসভা
দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য কীর্তনে যখন মুখরিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, তখন বার্মার অন্তর্ভুক্ত ‘মগের মুল্লুক’ এ আরাকানের বৌদ্ধ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয় তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মায়ানমারের উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে আরাকানের অবস্থান।
আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে ‘রোসাঙ্গ’ নামে অভিহিত করা হয়। মধ্যযুগে ধর্মসংস্কারমুক্ত ঐহিক কাব্যকথার প্রবর্তন করেন মুসলমান কবিগণ এবং তা আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়ে উঠে। একান্ত মানবিক প্রেমাবেদন-ঘনিষ্ঠ এসব কাব্য অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ সময়ের কবিগণের পুরোধা দৌলত কাজী বাংলা রোমান্টিক কাব্যধারার পথিকৃৎ হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।
প্র. বাংলা সাহিত্যে আরাকানকে কি বলা হয়?
উ. ‘রোসাঙ্গ’। সপ্তদশ শতকে এ অঞ্চল বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক প্রসারে বিশেষ অবদান রাখে।
প্র. আরাকান রাজসভার আদি কবি ও প্রথম বাঙালি কবি কে?
উ. দৌলত কাজী। তিনি লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যের নাম ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’। এটি হিন্দি কবি সাধনের ‘মৈনাসত’ কাব্য অবলম্বনে তিন খণ্ডে রচিত
প্র. আরাকান রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি কে?
উ. আলাওল । ‘পদ্মাবতী’ (১৬৪৮), ‘সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল’, ‘হপ্তপয়কর’, ‘সিকান্দরনামা’, ‘তোহফা’ তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা ।
প্র. পদ্মাবতী কে রচনা করেন?
উ. মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি ভাষায় রচিত ‘পদুমাবৎ’ অবলম্বনে আলাওল ‘পদ্মাবতী’ (১৬৪৮) রচনা করেন।
প্র. ‘চন্দ্রাবতী’ কে রচনা করেন?
উ. কোরেশী মাগন ঠাকুর। তিনি ছিলেন রোসাঙ্গরাজের প্রধানমন্ত্রী। তিনি আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ ও ‘সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল’ কাব্য রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন।
মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক
প্র. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কারা?
উ. পাঠান শাসকবর্গ ।
প্র. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণালি সময়কাল কোনটি?
উ. মোঘল যুগ।
প্র. বাংলা সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত কে?
উ. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।
প্র. বাহরাম খানকে ‘দৌলত উজির’ উপাধি প্রদান করেন কে?
উ. নৃপতি নেজাম শাহ সুর ।
প্র. কবি হাফিজকে বাংলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কে?
উ. গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ।
প্র. সম্রাট আকবরের সভাকবি কে ছিলেন?
উ. আবুল ফজল। তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আইন-ই-আকবরী’।
প্র. আরাকান রাজসভার উল্লেখযোগ্য কবি কারা?
উ, দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মরদন, আবদুল করিম খন্দকার।
প্র. কৃষ্ণনগর রাজসভার কবি কে ছিলেন?
উ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
যুগ সন্ধিক্ষণ (১৭৬০-১৮৬০)
আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মুখে কলকাতার হিন্দু সমাজে ‘কবিওয়ালা‘ এবং মুসলিম সমাজে ‘শায়ের’ এর উদ্ভব ঘটে। ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে ১৮৬০ সালে আধুনিকতার যথার্থ বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত এই ১০০ বছর বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে উৎকর্ষপূর্ণ কোনো নিদর্শন বিদ্যমান নেই।
প্র. যুগ সন্ধিক্ষণ বলতে কী বোঝায়?
উ. ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের তিরোধানের মাধ্যমে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে এবং ১৮৬০ সালে মাইকেলের সদর্প আগমনের মাধ্যমে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে। এ ১০০ বছর সাহিত্য জগতে চলছিল বন্ধ্যাকাল, ফলে এ সময়টুকুকে বলে ‘অবক্ষয় যুগ’ বা ‘যুগ সন্ধিক্ষণ’ ।
প্র. যুগ সন্ধিক্ষণের কবি / অবক্ষয় যুগের কবি কে?
উ. যুগ সন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্র. কবে কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটে?
উ. আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ।
প্র. কবিগান কী? (১৮তম বিসিএস লিখিত]
উ. দুই পক্ষের মধ্যে বিতর্কের মাধ্যমে যে গান অনুষ্ঠিত হতো তাই কবিগান । দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতাই এর বৈশিষ্ট্য। যারা এ গান গাইত (বিশেষত হিন্দু), তাদের বলা হতো কবিয়াল ।
১৮৫৪ থেকে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সর্বপ্রথম কবিগান সংগ্রহ করেন এবং ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন রেভারেন্ড জে. লং এ শ্রেণির রচনাকে ‘মুসলমানি বাংলা সাহিত্য’ বলে অভিহিত করেন।
প্র. কয়েকজন কবিয়ালের নাম বলুন?
উ. গোজলা গুই (কবিগানের আদি কবি), ভবানী বেনে, ভোলা ময়রা, হরু ঠাকুর, কেষ্টা মুচি, এন্টনি ফিরিঙ্গী, রামবসু, নিতাই বৈরাগী, নিধু বাবু।
প্র. শায়ের কারা?
উ. শায়ের আরবি শব্দ এবং এর অর্থ কবি। মুসলমান সমাজে মিশ্র (দোভাষী) ভাষারীতির পুঁথি রচয়িতাদের শায়ের বলা হতো। উল্লেখযোগ্য শায়েরগণ হলেন- ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোহাম্মদ দানেশ, মালে মুহম্মদ, আব্দুর রহিম, আয়েজুদ্দিন।
প্র. পুঁথি সাহিত্য কী ?
উ. অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত ‘আরবি-ফারসি’ শব্দ মিশ্রিত ইসলামী চেতনাসমৃদ্ধ সাহিত্যকে পুঁথি সাহিত্য বলে। পুঁথি সাহিত্যের প্রথম ও সার্থক কবি ফকির গরীবুল্লাহ ।
প্র. বটতলার পুঁথি কী ?
উ. অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত ‘আরবি-ফারসি’ শব্দ মিশ্রিত ইসলামী চেতনাসমৃদ্ধ সাহিত্য কলকাতার সস্তা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হয়ে এই ধারার কাব্য দেশময় প্রচারিত হয়েছিল বলে একে ‘বটতলার পুঁথি’ নামে অভিহিত করা হয়।এই শ্রেণির রচনাকে রেভারেন্ড জে. লং ‘মুসলমানি বাংলা সাহিত্য’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।
কবি কৃষ্ণরাম দাসের ‘রায়মঙ্গল’ (১৬৮৬) কাব্য পুঁথি সাহিত্যের প্রথম কাব্য হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও এতে পুঁথি সাহিত্যের সকল বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়নি।
প্র. দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রথম ও সার্থক কবি কে? (১৩তম
বিসিএস লিখিত।
উ. ফকির গরীবুল্লাহ। ‘আমীর হামজা’ (১ম অংশ), ‘জঙ্গনামা’, ‘ইউসুফ জোলেখা’, ‘সোনাভান’, ‘সত্যপীরের পুঁথি’ তাঁর উল্লেখযোগ্য মিশ্র ভাষারীতির কাব্য ।
প্র. দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের কবি সৈয়দ হামজার কাব্যগুলো কী কী? উ. ‘আমীর হামজা’ (১৭৯৫- ২য় অংশ), ‘জৈগুনের পুঁথি’ (১৭৯৭), ‘হাতেম তাই’।
প্র. টপ্পা গান কী?
উ. টপ্পা এক ধরনের গান। কবিগানের সমসাময়িককালে কলকাতা ও শহরতলিতে রাগ-রাগিনী সংযুক্ত এক ধরনের ওস্তাদি গানের প্রচলন ঘটেছিল, এগুলোই টপ্পা গান হিসেবে পরিচিত। টপ্পা থেকেই আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সূত্রপাত বলে অনেকের ধারণা।
প্র. বাংলা টপ্পা গানের জনক কে?
উ. রামনিধি গুপ্ত। তাঁর বিখ্যাত গান-
‘নানান দেশের নানান ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা’
প্র. পাঁচালী গানের জনপ্রিয় কবি কে?
উ. দাশরথি রায়। তিনি দাশুরায় নামে খ্যাত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পাঁচালী গান এদেশে জনপ্রিয় হয়েছিল।
প্র. শাক্ত পদাবলি কী?
উ. খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি শাক্তধর্মের উদ্ভব ঘটে এবং একে ঘিরেই শাক্তগীতি চর্চার একটি ক্ষীণ ধারার প্রচলন ঘটে। শাক্ত পদাবলি শক্তি বিষয়ক গান। এই পদগুলিতে যেমন লিরিকধর্মীতা আছে তেমনি আছে বাঙালির চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার কথা। এ পদাবলির প্রধান রস বাৎসল্য যা ১২ টি পর্যায়ে এবং দুটি ধারায় বিভক্ত।
রামপ্রসাদ সেন এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি শাক্ত পদাবলি বা শ্যামাসংগীত রচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ভক্তিভাব এবং রাগ ও বাউল সুরের মিশ্রণে এক ভিন্ন সুরের সৃষ্টি করেন, যা বাংলা সংগীত জগতে ‘রামপ্রসাদী সুর’ নামে পরিচিত। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁকে ‘কবিরঞ্জন’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হলো- ‘বিদ্যাসুন্দর’, ‘কালীকীর্তন’

 Sopner BCS Sopner BCS: We fuel your BCS dreams
Sopner BCS Sopner BCS: We fuel your BCS dreams